সিলেট ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
প্রকাশিত: ৪:০৩ অপরাহ্ণ, ডিসেম্বর ৩০, ২০২৪
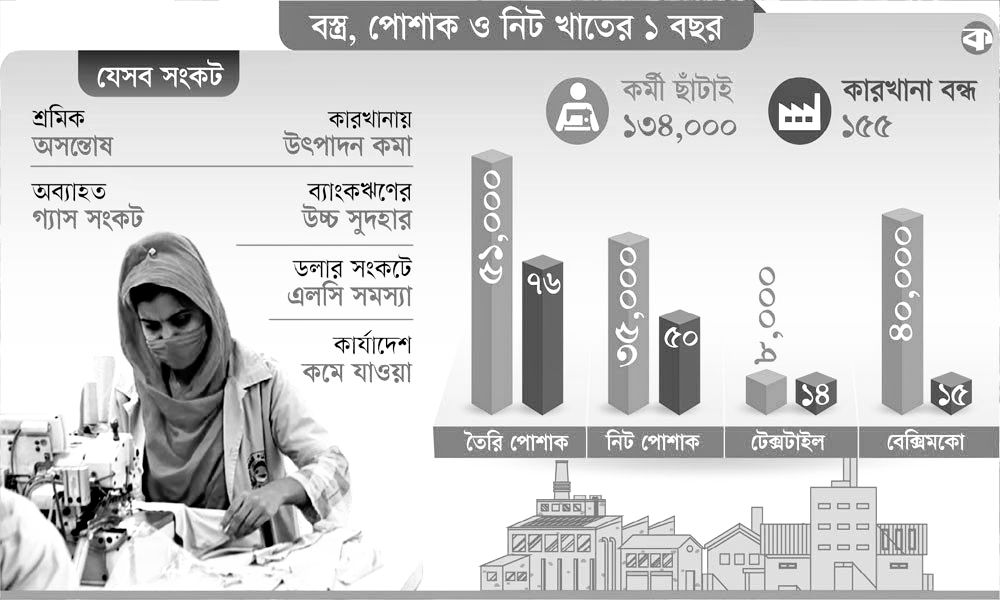
রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংকট ও শিল্প-সেবা-কৃষি খাতে স্থবিরতার কারণে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনীতি বৃদ্ধির গতি হ্রাসের পূর্বাভাস দিয়ে বলেছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৪ শতাংশ বাড়বে। বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার কলকাঠি নাড়া অন্যতম এই সংস্থাটি এর আগে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫ দশমিক ৭ শতাংশের কথা বলেছিল। সংস্থাটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ৫ দশমিক ২ শতাংশ করেছিল, যা সরকারের অস্থায়ী প্রাক্কলন ৫ দশমিক ৮২ শতাংশের তুলনায় কম।
গত জুলাই ও আগস্টে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৫ দশমিক ১ শতাংশে নামিয়ে আনার দুই সপ্তাহ পর সংশোধিত বিশ্বব্যাংকের এই পূর্বাভাস প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, দীর্ঘ সময় ধরে কম বিনিয়োগ, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, খেলাপি ঋণের লাগামহীন ধারা আর সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুতর কিছু দুর্বলতা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে।
তার ওপর মাস চারেক ধরে চলা অর্থনীতি চরম স্থবিরতায় জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও সংকুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। তারা মনে করেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমায় হতাশা অনুভূত হলেও, হা-হুতাশ করার কিছু নেই। বরং ভুলভাল তথ্য-পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে না হয়ে সত্যি সত্যি ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলে, তা নানামুখী সংকটে থাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য হবে বড় এক সুখবর।
প্রবৃদ্ধি বিষয়ক বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এই পূর্বাভাসের গভীরে যাওয়ার আগে বলে নেওয়া ভালো, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্ট ¯্রফে পরিসংখ্যানের এক খেলা, যার পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ‘উন্নয়ন অর্থনীতি’ নামে অর্থশাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখাই জন্ম লাভ করেছে। শাস্ত্রীয় অর্থে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবার উৎপাদন বৃদ্ধি বোঝায়।
সাধারণত, কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্ট (জিডিপি) বৃদ্ধির শতকরা হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ১৬৭৬ সালে স্যার উইলিয়াম পেটি, ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথ এবং পরবর্তী সময়ে ডব্লিউ ডব্লিউ রস্টোসহ আরও কিছু অর্থনীতিবিদের নানা তত্ত্বের কল্যাণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়টি সমসাময়িক বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঢুকে পড়া দেশগুলোর রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা।
কারণ, এই পদ্ধতিতে তারা পরিসংখ্যানের নানা মারপ্যাঁচে জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে তাদের গৃহীত-অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি ও পথ চলার কার্যকরতা ও সাফল্য সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারেন। সত্যিকার অর্থে, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায় না। তা-ই যদি হতো, তাহলে গত কয়েক দশক ধরে জাতীয় আয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্বের উন্নত দেশ তো বটেই অন্যান্য এশীয় দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে যেতে দেখা যেত না।
মানবসম্পদের নিম্নমান, দুর্বল অবকাঠামো, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের স্থবিরতা, খাতনির্ভর বাজারে একরাশ ব্যর্থতা, তুলনামূলকভাবে নিম্ন বৈদেশিক বাণিজ্য, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি এবং নীতিনির্ধারকদের নীতিহীনতা চর্চার সংস্কৃতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনমানে বহুমুখী ব্যবধান কমানো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চতর ধাপে যেতে প্রধান বাধা হয়ে আছে।
এমন বাস্তবতায় কী কী গতিময় উপাদানের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কী কী উপাদান উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধির ভিত্তি তৈরি করবে, সেটি অনুসন্ধান করা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
অর্থনীতিতে নানা সমস্যা সত্ত্বেও দীর্ঘসময় ধরে বাংলাদেশের অর্তনীতিতে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী প্রবৃদ্ধি প্রবণতা অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষকেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। যেমন সত্তরের দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করা নরওয়ের অর্থনীতিবিদ ফাল্যান্ড ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পারকিনসন ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ: টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট’ বইয়ে যদিও লেখেন, ‘যদি বাংলাদেশে উন্নয়নের উদ্যোগ সফল করা যায় তবে এ ধরনের উদ্যোগ যেকোনো দেশেই সফল করা যাবে।’
তারপরও ২০০৭ সালে এসে তারা পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসে বলতে বাধ্য হন, ‘তিন দশক এবং তার বেশি সময়ের সীমিত ও বর্ণাঢ্য অগ্রগতির ভিত্তিতে মনে হয়, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব; তবে এ সম্ভাবনা নিশ্চিত নয়।’ তাদের মতো অনেকের মনের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, নির্মোহ অর্থনীতিবিদদের মূল্যায়নে।
তারা মনে করেন, প্রবৃদ্ধিতে মাপার কথা দেশে সারা বছরে যত চূড়ান্ত দ্রব্য-পণ্য ও সেবা উৎপাদন হয় তার বাজারমূল্য। কিন্তু বাংলাদেশের জিডিপিতে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক খাতের উৎপাদন ও আয়, নারীর গৃহস্থালি শ্রম-উদ্ভূত নবসৃষ্ট সেবা ও দ্রব্য, ঘুষ-দুর্নীতি-উদ্ভূত আয়, কালোটাকার পরিমাণ, পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ, মূল্য আছে কিন্তু মূল্যায়িত হয় না অথবা অবমূল্যায়িত হয় এমন অনেক কিছুই, নবসৃষ্ট দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে প্রকৃতি ও পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার বিয়োগযোগ্য আর্থিক মূল্য প্রভৃতি হিসাবে নেওয়া হয় না।
ফলে জিডিপি ঊর্ধ্বমুখী বা উচ্চ দেখায়। এ কারণে নির্মোহ অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের মোট দেশজ উৎপাদন বা অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধিকে রাজনীতিবিদ ও মূলধারার অর্থনীতিবিদদের সৃষ্ট ‘সুবিধার প্রবৃদ্ধি’ বলে অভিহিত করেন। কাজেই এই প্রবৃদ্ধি বাড়লেই কি, কমলেই বা কি! এমন প্রবৃদ্ধি চিত্র দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনমানের অবস্থা বোঝা যায় না। কিংবা মূল্যায়ন করা যায় না সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রকৃত অবস্থা। বরং ৫, ৬, ৭ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ৫ শতাংশ আয় বৃদ্ধি ও ৮-১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতির তথ্য দিলে তাদের জীবনমানের অবস্থা সহজে বোধগম্য হয়।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হিসাব-নিকাশ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক থাকলেও প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া দুর্বল ও অনিশ্চয়তাময় এক পরিবেশই নির্দেশ করে, যেখানে দেশি ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগই নিরুৎসাহিত হয়। ফলে প্রবৃদ্ধির সুযোগ আরও সংকুচিত হয়, অর্থনীতির কোনো খাত-ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় না। এ কারণে বলা হয়, প্রবৃদ্ধি হ্রাস একটি সংকুচিত অর্থনীতি তুলে ধরে, যেখানে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সংকুচিত হয়।
উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যস্ফীতির মধ্যে যদি প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়, তাহলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, যা জীবনযাত্রার মান আরও কমিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে তা স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার খরচের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাংলাদেশে এমনটা হলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
বাংলাদেশের ওপর দিয়ে নীরবে বয়ে চলা এই বিষয়গুলোর আলোকে অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই পণ্যের দাম স্থিতিশীল করার দিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা পুনরুদ্ধার করা এবং একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি। এখানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির চীনের উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। চীন যখন ১৯৭৮ সালে তার অর্থনীতিকে সংস্কার করে উদারনীতি গ্রহণ শুরু করে, তখন থেকেই দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বছরে গড়ে ৯ শতাংশের বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে।
বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে পরিণত হওয়া এই দেশটি শুধু ২০২০ সালের করোনা মহামারির সময় মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল, যা কয়েক দশকের মধ্যে ছিল দেশটির সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি অর্জনের রেকর্ড। কিন্তু এর পরের বছরই অর্থাৎ ২০২১ সালে দেশটির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং অনেককে অবাক করে দিয়ে ৮ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। কিন্তু পরের বছর ২০২২ সালে এসে দেশটির প্রবৃদ্ধি কমে গিয়ে মাত্র ৩ শতাংশে দাঁড়ায়।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে চীনের সরকার জানায়, ২০২৩ সালে দেশটি ৫ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা ছিল প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনায় বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির মধ্যে ভারতের পরেই দ্বিতীয়। তবে চীনের অর্থনীতি ভারতের চেয়ে পাঁচগুণ বড়। চীনের প্রবৃদ্ধির এ রকম হ্রাস-বৃদ্ধি কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য দেশগুলোর চীনবিরোধী নানা নীতিমালা, বৈশ্বিক মেরুকরণ ও যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গত পাঁচ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে প্রথম চীন থেকে বড় হারে বিদেশি বিনিয়োগ অন্যত্র চলে যাওয়া।
এতে করে চীনে তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হারে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে, যা গত বছরের জুনের তুলনায় ২০ শতাংশেরও বেশি। এ ছাড়া ২০২৪ সালের শুরুতে দেশটির শেয়ারবাজারের দামেও ধ্বস দেখা গেছে, যা গত ৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বলে রাখা ভালো, ২০২০-২১ সময়কালের করোনাকালে কর্মহীন জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠান, রাজ্য ও স্থানীয় সরকারকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা দিয়েছিল।
বিপরীতে চীন তখন আর্থিক নীতি আরও সংকোচন করে। এর ফলে চীনে মুদ্রাস্ফীতি তেমন কোনো সমস্যা হয়ে উঠতে না পারলেও দেশটির অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেশটিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কয়েক বছর ধরে এমন উত্থান-পতন লক্ষ করা যাচ্ছে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি চীনের মতো বিশালও নয়, শক্তিশালীও নয়। এ কী কী গতিময় উপাদানের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কী কী উপাদান উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধির ভিত্তি নিশ্চিত করতে পারে, তা বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নীতিনির্ধারণী দায়িত্বে থাকা বেশ কয়েকজন জ্ঞানাভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ সময় ও সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই ভালো বুঝবেন এবং সেই আলোকে তাঁরা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি টেকসই অর্থনীতিতে রূপান্তরের পথে নিয়ে যাবেন- এই আশা সবাই করেন। আর যদি অর্থনীতি শাস্ত্রের জ্ঞানী-গুণী এই মানুষেরা তা না পারেন; তাহলে তা হবে আমাদের জন্য বড় এক দুর্ভাগ্য।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়;
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান
ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com
মোবাইল +8801716599589
৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
© RP News 24.com 2013-2020
Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি
