সিলেট ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
প্রকাশিত: ১২:৩০ পূর্বাহ্ণ, এপ্রিল ২০, ২০২৫
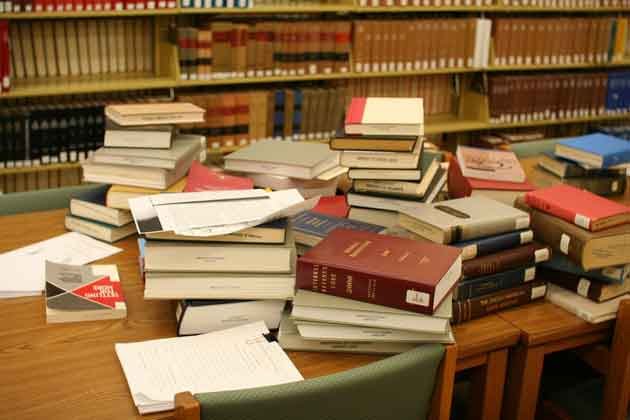
বিশেষ প্রতিনিধি | ঢাকা, ২০ এপ্রিল ২০২৫ : আগামী ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস বা বিশ্ব গ্রন্থ দিবস (এছাড়া বিশ্ব বই এবং কপিরাইট দিবস, বা বইয়ের আন্তর্জাতিক দিবস নামেও পরিচিত) হল পড়া, প্রকাশনা এবং কপিরাইট প্রচারের জন্য জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন (ইউনেস্কো) দ্বারা আয়োজিত একটি বার্ষিক দিবস।
ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।
বই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো, বই পড়া, বই ছাপানো, বইয়ের কপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো। সর্বোপরি প্রকাশক লেখক পাঠকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা।
বিশ্ব বই দিবসের মূল ধারণাটি আসে স্পেনের লেখক ভিসেন্ত ক্লাভেল আন্দ্রেসের কাছ থেকে। ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল মারা যান স্পেনের আরেক বিখ্যাত লেখক মিগেল দে থের্ভান্তেস। আন্দ্রেস ছিলেন তার ভাবশিষ্য। নিজের প্রিয় লেখককে স্মরণীয় করে রাখতেই ১৯২৩ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে আন্দ্রেস স্পেনে পালন করা শুরু করেন বিশ্ব বই দিবস। এরপর দাবি ওঠে প্রতিবছরই দিবসটি পালন করার। অবশ্য সে দাবি তখন নজরে আসেনি কারোই। অপেক্ষা করতে হয় দিনটি বাস্তবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য।
অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো দিনটিকে বিশ্ব বই দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং পালন করতে শুরু করে।
এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
উল্লেখ্য, ২৩ এপ্রিল শুধুমাত্র বিশ্ব বই দিবসই নয়,
শেক্সপিয়র, সত্যজিৎ রায়, ইনকা গার্সিলাসো ডে লা ভেগাসহ প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসও। আর এ কারণেও ২৩ এপ্রিলকে বিশ্ব বই দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন অনেকেই।
বই শব্দটি আসলেই চোখের সামনে ভেসে উঠে পুরান ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চলে কাগজীটোলা, শ্যামবাজার কিংবা ফরাশগঞ্জের রাস্তা। রাস্তার পাশেই অধিকাংশ বাড়িই পুরনো। আর বেশিরভাগ বাড়ির নিচতলায় বই বাঁধাই কারখানা- বই বাঁধাইয়ের কাজ চলে। জানুয়ারির বই উৎসব ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা কিংবা সারা বছর ধরে ছাপা বিভিন্ন প্রকাশনীর বিভিন্ন প্রকারের বই বাঁধাইয়ের কাজ হয় পুরানো ঢাকার একটা বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। আমরা সুন্দর বাঁধাই বই হাতে পাই, জানিনা বাঁধাই করলো কে? জানিনা তার জীবন গল্পটা কি? বই বাঁধাই শ্রমিকের জীবন গল্প অনেকেরই অজানা।
পুরনো বাড়ী। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ ঘর। স্যাঁতসেতে ঘরটাতে বই বাঁধাইয়ের কাজ করে। এরা বই বাঁধাই শ্রমিক নামে পরিচিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিদ্যুতের আলোতে চলে বই বাঁধাইয়ের কাজ। পাঠ্যবই থেকে শুরু করে কবিতা-গল্প-উপন্যাসসহ সবই বাঁধেন। শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ বয়সের মানুষরাও এ পেশায় জড়িত। এদের কাজের ধরনও আলাদা। কেউ ছাপানো কাগজ ভাঁজ করেন, কেউবা ভাঁজ করা কাগজ সাজিয়ে মেছেল তোলেন। কেউ সুঁইয়ে সুতা লাগিয়ে ফর্মাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেন, যাতে ফর্মার কোনো ওলট-পালট না হয়। এইভাবে মলাট লাগানো, তারপর মেশিনে বইয়ের তিনধার কেটে ফিনিশিং দেওয়া ও প্যাকেজিং করার পর সেই বই আমরা বাজারে পাই। পাঠকের বইটি পড়ার সময় যাতে বিষয়ের ধারাবাহিকতার কোনো ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য শ্রমিকদের খুবই সতর্ক থাকতে হয় পুরো সময়টাতে।
পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজে শ্রমিকরা আসে মূলত টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, সিরাজগঞ্জের চৌহালী ও মানিকগঞ্জের দৌলতপুর অঞ্চল থেকে। অভাবের তাড়নায়, জীবন ধারণের তাগিদে তারা ঢাকায় আসে। শুরু করে বই বাঁধাইয়ের কাজ।
কাজের বিভিন্ন ধরণ আছে। কেউ করে রোজ অনুযায়ী আবার কেউ দিন চুক্তি হিসেবে। সকাল ৮ থেকে শুরু হয় কাজ। সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এক রোজ এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০ পর্যন্ত দুই রোজ আর রাত ১০টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হাফ রোজ। একজন শ্রমিক সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে তাহলে তার মোট আড়াই রোজ কাজ হয়। এই বাজারে আড়াই রোজ কাজ করে তাদের সংসার চলে না। একজন দক্ষ বই বাঁধাই শ্রমিক আড়াই রোজ অর্থাৎ ১৬ ঘন্টা কাজ করলে প্রতিদিন সর্বসাকুল্যে ৩৫০-৪০০ টাকা মজুরি পায় একজন শ্রমিক। এর মধ্যে সারাদিনের খাবার বাবদ তাকে খরচ করতে হয় একেবারে কম করে হলেও ১০০ টাকা। তাহলে সারা মাস কাজ করলে খাবার খরচ বাদ দিয়ে তার হাতে থাকে মাত্র ৭৫০০-৯০০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে নিজের ওষুধপত্র ও হাত খরচ বাদ দিলে পরিবারের জন্য গ্রামে পাঠাতে পারে খুবই সামান্য টাকা। একজন দক্ষ শ্রমিকের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অদক্ষ ও শিশু শ্রমিকদের কী অবস্থা তা অনুমান করা যায়।
কারাখানাগুলোতে ১০/১২ বছরের শিশুরা খাবার ও মাসে ২০০০/৩০০০ টাকার বিনিময়ে দিন রাত কাজ করে, যে সময়ে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা! একমাত্র ঈদ উৎসব ছাড়া অন্য কোনো ছুটি তাদের নেই। সকল ধরনের উৎসব বোনাস থেকে তারা বঞ্চিত। উৎসবের সময় শুধুমাত্র মাসের মজুরি নিয়ে শুষ্ক মুখে শ্রমিকরা বাড়ি ফেরে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন কিংবা শুক্রবার তাদের কাজ কখনও বন্ধ হয় না।
বাঁধাই শ্রমিকরা কাজের জায়গাতেই খায়। কাজ শেষে জায়গা পরিষ্কার করে তারা লাইন দিয়ে ঘুমাতে যায়। কাজের মৌসুমে কারখানায় যখন বেশী কাগজ থাকে তখন তারা কাগজের উপরেই ঘুমায়। আলো-বাতাসহীন অপরিষ্কার ঘর, স্যাঁতসেতে মেঝে আর কাগজের ধুলো-ময়লা — এর উপরই হাড়ভাঙা খাটুনির পর প্রায় নেতিয়ে পড়া শরীর নিয়ে শুয়ে পড়া।
অত্যাবশ্যকীয়ভাবে লেগে থাকে হাঁপানি, চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগের প্রকোপ। কেউ অসুস্থ হলে বিশ্রামের জন্য কোনো জায়গা নেই। অসুস্থ হয়ে বইয়ের বান্ডিলের উপর বিশ্রাম নিতে গেলেও মালিকের গালিগালাজ শুনতে হয়। কারখানায় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই। লাইনের ময়লা, গন্ধযুক্ত পানি পান করে। এর ফলে তারা অনেকসময় ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়, তারা পেটের পিড়ায় ভুগেন। বই বাঁধাই শ্রমিকরা কাজের সময় কোনো দূর্ঘটনার শিকার হলে বা মৃত্যু হলে তার দায়- দ্বায়িত্ব কারখানার মালিক বহন করে না।
সবশেষে- বই বাঁধাই শ্রমিকের এত কষ্টের পরেই। প্রকাশক লেখক পাঠক সদ্য ভুমিষ্ট হওয়া সন্তানের মতো নতুন বই হাতে পায়। কিন্তু আড়ালেই থেকে যায় বই বাঁধাই শ্রমিকের জীবন গল্প….
বিশ্ব বই দিবস বা বিশ্ব গ্রন্থ দিবসের সফলতা কামনা করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক, সাপ্তাহিক নতুন কথা’র বিশেষ প্রতিনিধি, আরপি নিউজের সম্পাদক ও বিশিষ্ট কলামিস্ট কমরেড সৈয়দ আমিরুজ্জামান বলেন, “আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের হাত ধরেই সত্তর দশকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। হাটি হাটি পা পা করে ৪৬ বছর পূর্ণ হয়েছে তার। স্বাধীন, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল মূল্যবোধসম্পন্ন, শক্তিশালী মানুষ তৈরির লক্ষ্যেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ৪৬ বছর থেকে কাজ করছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যাসহ বিশ্বজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর পঠন-পাঠন এই কাজের অন্তর্ভুক্ত।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কোনো গৎ-বাঁধা, ছক-কাটা, প্রাণহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি সপ্রাণ সজীব পরিবেশ- জ্ঞান ও জীবন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে পূর্ণতর মনুষ্যত্বে ও উন্নততর আনন্দে জেগে ওঠার এক অবারিত পৃথিবী। এক কথায়, যাঁরা সংস্কৃতিবান, কার্যকর, ঋদ্ধ মানুষ- যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, সৌন্দর্যপ্রবণ, সত্যান্বেষী; যাঁরা জ্ঞানার্থ, সক্রিয়, সৃজনশীল ও মানবকল্যাণে সংশপ্তক ‘বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র; তাঁদের পদপাতে, মানসবাণিজ্যে, বন্ধুতায়, উষ্ণতায় সচকিত একটি অঙ্গন।
মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং বিভিন্নবিষয়ক জ্ঞান ও রুচিশীল সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটানো এর উদ্দেশ্য।
২৩ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্ব বই দিবস বা বিশ্ব গ্রন্থ দিবস জ্ঞানপিপাসু প্রতিটি মানুষের অবারিত অংশগ্রহণে আলোকিত মানুষ’ গড়ার আন্দোলন তরান্বিত হোক।”
পৃথিবীতে ‘বই’–এর ধারণা কীভাবে এল, বিশ্বের প্রথম বই কোনটি, বেস্টসেলার বইয়ের ধারণা এল কেমন করে? বই এল কোত্থেকে? এত মানুষ বই কেনে, তারা কি পড়েও?
বইয়ের ধারণা
বইয়ের উৎস নিয়ে আলাপ করতে হলে কাগজের ইতিহাসের কথা আসবেই আসবে। কাগজে ছাপা হয়ে বই কোনো দিন মানুষের হাতে হাতে ঘুরবে বা শেলফে শোভা পাবে, এমনটা খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালে কেউ হয়তো ভাবেনি। তবে সন্দেহ নেই, তাদের অজান্তে ভাবনাটির বীজ তখনই পোঁতা হয়েছিল। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় মানুষ তখন কাদা দিয়ে সমতল আয়তক্ষেত্র বানিয়ে নানান চিহ্ন এঁকেছিল। কাদার ওপরে আঙুল চালিয়েছিল ভাবনাকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০০ সালে শুরু হলো প্যাপিরাসের ব্যবহার। অনেকের ধারণা, প্যাপিরাস এক রকমের পাতা। প্রকৃতপক্ষে গাছ থেকে উৎপন্ন হলেও প্যাপিরাস নীল নদের আশপাশের জলা জায়গায় জন্মানো প্যাপিরাসগাছের কাণ্ডের ভেতরের অংশ। গাছটির পিথ (কাণ্ডের কেন্দ্র) লম্বালম্বি পাতলা করে কেটে শুকিয়ে নিয়ে মিসরীয়রা তাতে লিখত। গ্রিক আর রোমানদের হাজার বছর আগেই এই প্রযুক্তি রপ্ত করেছিল তারা।
লেখার উপাদান ও কায়দা
৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আসতে আসতে কিসে লেখা হবে, তার চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল কীভাবে লেখা হবে, এই বিতর্ক, মানে ডান থেকে বাঁয়ে নাকি বাঁ থেকে ডানে? যে যার সুবিধামতো নিয়ম তৈরি করল। আরবি আর হিব্রু ভাষা ডান থেকে বাঁয়ে লেখার প্রচলন হলেও বেশির ভাগ ভাষা বাঁ থেকে ডান দিকটাকে বেছে নিল। তবে কেউ নিচ থেকে ওপরে, আবার কেউ ওপর থেকে নিচে—বিচিত্র কায়দায় লেখা অব্যাহত রাখল। তারপর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে কেবল লেখালেখির উপাদানের। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাসের সময়ে লেখা হতো বাছুর, ভেড়া বা ছাগলের চামড়ায়। ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে মোম দিয়ে বানানো সমতলে আর কাগজে লেখা বসেছে। চীনের মানুষেরা অবশ্য কিছু আগে থেকে জিনিসপত্র মোড়ানোর কাজে কাগজ ব্যবহার করত। কাগজে লেখার সঙ্গে টুকরো ছবি জুড়তে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ এসে পড়ল। এভাবে চীনে ছবিসহ বই ছাপা হলো ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে। তখন একদিকে চীনে ব্লক প্রিন্ট বই ছাপানো হচ্ছে, আরেক দিকে একই চেষ্টা চলছে ইউরোপে। ১২৫০ সালে মিসরে আর ১৪৫০ সালের মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি স্থানে অক্ষর বসিয়ে বই ছাপানোর কাজ শুরু হলো। এশিয়ার এদিকটায় তখন গাছের বাকল, কলাপাতা বা তালপাতায় হস্তাক্ষরে পুঁথি লেখা হতো। প্রক্রিয়াজাত করে লেখার পর সংরক্ষণের উপায় তাতে পুঁথির ছন্দেই নানাভাবে লেখা থাকত, যেমন বাংলায় বললে দাঁড়ায় পুঁথিকে পুত্রের ন্যায় পালবে, শত্রুর ন্যায় বাঁধবে। তবে সমসাময়িক ১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গ বাইবেল প্রথম ছাপানো বইয়ের মর্যাদা পেয়েছে। শিল্পসম্মতভাবে তৈরি ৪২ লাইনের বাইবেল হিসেবে খ্যাত বইটির ২১টি কপি এখনো বিদ্যমান। কখনো বিক্রির জন্য উন্মুক্ত হলে নিঃসন্দেহে ওগুলোই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি বই।
মূল্যবান বই
আর্থিক মূল্যের কথা বলতে গেলে অবশ্য লেওনার্দো দা ভিঞ্চির কোডেক্স লিসেস্টার-এর কথা আসে, যা প্রকৃতপক্ষে লেওনার্দোর ৩০টি বৈজ্ঞানিক গবেষণার খসড়া খাতা। ১৯৯৪ সালে নিলামে উঠলে বিল গেটস ৩০.৮ মিলিয়ন ইউএস ডলারে কিনে নেন। আপাতত সর্বোচ্চ মূল্যের ছাপানো বই হলো উত্তর আমেরিকায় প্রকাশিত প্রথম বই, বে সাম (১৬৪০)। ২০১৩ সালে নিলাম হলে এর প্রথম সংস্করণের ১১টির মধ্যে একটিই বিক্রি হয়েছিল ৪২.২ মিলিয়ন ইউএস ডলারে।
‘বেস্টসেলার’ ও বহুল পঠন
মূল্যের সঙ্গে বইয়ের বহুল পঠনের সম্পর্ক প্রায়ই থাকে না। কারণ, যে বই সবচেয়ে বেশি পড়া হয়, তা হতে হয় সুলভ। যেমন বহুল পঠিত তিনটি বই হলো বাইবেল, কোটেশন ফ্রম চেয়ারম্যান মাও সে তুং আর হ্যারি পটার। ‘হ্যারি পটার সিরিজ’ একদিকে সবচেয়ে বেশি পড়া হয়েছে, অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি নিষিদ্ধও হয়েছে। হাতে–কলমে জাদুটোনার ধারণা নিয়ে ভবিষ্যতে শিশুদের বাস্তববিমুখ হওয়ার সম্ভাবনা আঁচ করে বইটি অনেক দেশ নিষিদ্ধ করেছে। সে যা–ই হোক, ‘সর্বাধিক বিক্রীত’ ধারণাটি এখন বহুল প্রচলিত। এতে পাঠককে বইটির মাহাত্ম্য সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয় বটে, তবে ধারণাটি মূলত ব্যবসাসফল একটি পণ্যের পরিচয় জানায়। বই যতটা জ্ঞান বিতরণের হাতিয়ার, ঠিক ততটাই পণ্য। এর আকার-আকৃতি আছে, আছে মনহরণ মোড়ক আর গায়ে মূল্যও আছে সাঁটা। সুতরাং তাকে পণ্য না বলে উপায় নেই। পণ্যের বিপণন লাভজনক হলে বিক্রেতা, মূলত প্রকাশক, ক্ষেত্রবিশেষে লেখকও লাভবান হন। ব্যবসার সফলতা জানাতে তাই ১৮৮৯ সালে প্রথম ‘বেস্টসেলার’-এর ধারণা আসে অ্যালিস ব্রাউনের ফুলস অব নেচার বইটি প্রথম বেস্টসেলার হিসেবে পরিচিতি পায়।
পাঠের মহিমা
সত্যিই কি অনেক মানুষ বই পড়ে? পেঙ্গুইন প্রকাশনীর সমীক্ষা অনুযায়ী ৬৮ শতাংশ বই কেনেন নারী ক্রেতা। অপ্রাসঙ্গিকভাবে সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণনার সেই নারীর কথা মনে পড়ে, বই কেনার কথা বললে যিনি বলেছিলেন, ‘ওটিও তো ওঁর একটি আছে।’ কিন্তু ধরা যাক, যারা বই কেনে, তারা অনেকে পড়েও। এই যেমন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখা যায়, ৭৩ শতাংশ আমেরিকান বই পড়ে আর তাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ পড়ে কাগুজে বই। বাংলাদেশে এমন একটি সমীক্ষা আমাদের হতাশ করবে বলেই কি তা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা আমরা কেউ বলি না? বই পড়া নিয়ে প্রচুর সমীক্ষা হয়। কিংস্টোন বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে যারা কল্পকাহিনি পড়ে, তারা সমাজের অন্য মানুষদের তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ, সহানুভূতিশীল ও উদার মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের ইতিবাচক চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। এ রকম ধারণা সত্য হতেই পারে। কারণ, সম্ভবত একটি বই একজন মানুষকে আমূল বদলে দিতে সক্ষম। কালজয়ী দীর্ঘ উপন্যাস কিংবা চাঞ্চল্যকর তথ্যসমৃদ্ধ বই পড়তে শুরু করার মুহূর্তের মানুষটি আর শেষ পাতা পড়ে নিয়ে বন্ধ করে রাখা পাঠক কিছুতেই এক মানুষ নন। তিনি হয়তো জানেন না পাতার পর পাতা তাঁকে ভেতরে–ভেতরে নতুন করে সাজিয়েছে। কেবল ব্যক্তিগত পরিশোধন নয়, সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নের জন্যও বইকে দায়ী করা যেতে পারে, যেমন জর্জ অরওয়েলের ১৯৮৪, স্টিফেন হকিংয়ের আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম কিংবা কার্ল মার্ক্স ও অ্যাঙ্গেলসের দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো—এ রকম বই কখনো বদলেছে আমূল সমাজ, কখনো প্রযুক্তি বদলে প্রবর্তন করেছে নতুন জীবনপদ্ধতি। অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, পাঠের অভ্যাস মানুষকে দীর্ঘজীবী করে, মানসিক চাপ আর আলঝেইমারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়।
প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্ট দিনে গড়ে একটা করে বই পড়তেন। কিন্তু বইয়ের মধ্যে আসলে থাকেটা কী যে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়? বলতে গেলে মানুষ যা জানতে চায় বা পছন্দ করে, তা-ও যেমন বইয়ে থাকে, আবার যা জানবে বলে ভাবেনি, তা-ও থাকে—যা পড়ে সে চমকে উঠতে পারে। চমকে উঠতে পারে বইয়ে পরিবেশিত তথ্য বা পরিবেশনার বৈচিত্র্যের কারণে। কিংবা বইটির মাধ্যমে অজানা জীবনের অলিগলিতে অবলীলায় হেঁটে আসার কারণে।
লেখক ও রচনা
বইয়ের চিরাচরিত আবেদন ছাড়াও এমনিতে পাঠককে চমকে দিয়ে কালজয়ী আখ্যা পেতে লেখকেরাও কম যান না। দস্তয়ভস্কি কিংবা ফকনার যেমন অনেক রচনায় প্যারার পর প্যারা দাঁড়ি-কমাবিহীন বর্ণনা চালিয়েছেন, তবে জিতেছেন অবশ্য ভিক্টর হুগো—লা মিজারেবল উপন্যাসে ৮২৩ শব্দের দীর্ঘতম বাক্যের কারণে। আবার কেবল লেখার কায়দা নয়, বিষয়বস্তু দিয়েও লেখক পাঠককে ভড়কে দিতে পারেন। যেমন জেমস জয়েসের ইউলিসিস নিয়ে বহু গবেষণামূলক বিতর্ক আছে, লেখক কি অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, নাকি কেবলই এলেবেলে হাস্যরস? বিতর্কগুলো যেকোনো পাঠককে দ্বিধা আর রহস্যে নিমজ্জিত করতে পারে। বইয়ের পেছনে লেখকের বীভৎস রকমের পরিশ্রমের কথা চিন্তা করলেও কখনো স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক নাটক রক্তকরবীর খসড়া লিখেছিলেন ১০ বার। অন্যদিকে তলস্তয় কমবেশি সাড়ে তিন কেজি ওজনের ওয়ার অ্যান্ড পিস উপন্যাসের বেশির ভাগ অংশের খসড়া করেছিলেন অন্তত ১৫ বার।
কাগজ আবিষ্কার হলেও তার ওপরে অক্ষর বানিয়ে ছাপার কৌশল আবিষ্কার হতে বহু সময় লেগে গেছে। তত দিনে তৈরি হয়েছে হাতে লেখা বই, যা চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত হতো। হাতে লেখা কোরআন শরিফ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ওদিকে টাইপরাইটারের আগমনে একসময় হাতে কম্পোজ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত মার্ক টোয়েনের লাইফ অন দ্য মিসিসিপি বইটি ছিল টাইপরাইটারে কম্পোজ করা প্রথম বই। বর্তমানে লেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির অভাব নেই। অথচ এখনো অনেক লেখক হাতেই লিখছেন, এমনকি কালির কলম দিয়ে—অভ্যাস বলে কথা! লেখক আদতে ব্যক্তি বলেই তাঁর নিজস্বতা আছে, আছে নিজের স্টাইলের স্বাধীনতাও। যেমন ভার্জিনিয়া উলফ দাঁড়িয়ে লিখতেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে লিখতে বসতেন আর টানা লিখে যেতেন। ড্যান ব্রাউন দ্য ভিঞ্চি কোড লেখার সময় প্রতিদিন ভোর চারটায় উঠে লিখতে বসতেন আর প্রতি ৬০ মিনিট পরপর দিতেন ৫০টা বুকডন।
কিন্তু কেবল নিয়ম মানলেই কি একটি কালজয়ী সৃষ্টি সম্ভব? ধরা যাক, বড় আকৃতির একটি উপন্যাসে ৯০ হাজার শব্দ থাকবে। মানুষের গড় টাইপিং স্পিডে (১ ঘণ্টায় ১৮৯ শব্দ) লিখলে মাত্র ৪৭৫ ঘণ্টায় উপন্যাসটি লেখা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো, সাহিত্য গণিত নয়, তাই সবকিছু সময়মতো হলেও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। অমূল্য সাহিত্যে থাকতে হবে বিশেষ কিছু, যা পাঠককে আঁকড়ে ধরবে, বিস্মিত করবে, প্রশান্তি দেবে, আবার তাকে ঢেলে সাজাবে। সবচেয়ে বড় কথা, যেকোনো কালে, যেকোনো পরিস্থিতিতে যার সাহিত্যমূল্য অটুট থাকবে। আর এই কালোত্তীর্ণ সাহিত্য নিয়মকানুনের ধার ধারে না। জে আর আর টোলকিন কি-বোর্ডে মাত্র দুই আঙুলের চাপে লর্ড অব দ্য রিং-এর ট্রিলজি লিখেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জীবনানন্দ দাশ চরম দারিদ্র্য-জর্জরিত অবস্থায় যুগান্তকারী সাহিত্য রচনা করেছেন, চোখের জ্যোতি হারিয়েও হোর্হে লুইস বোর্হেস মুখে বলে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি।
বিক্রি ও মানদণ্ড
বইয়ের প্রচুর বিক্রির জন্য চাকচিক্যের চেয়ে ভেতরের পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ। সাদামাটা প্রচ্ছদের উপদেশ ও ন্যায়নীতির কথা প্রচার করা বই বরাবর বিক্রির তালিকার শীর্ষে থাকে, সে হোক ডেল কার্নেগি বা মাও সে তুং–এর আমল কি হোক আজকের। এতে অন্তত একটি বিষয় আন্দাজ করা যায়, তা হলো মানুষ ভালো হতে চায়। না চাইলেও, মানুষ ভালো কথা পড়তে পছন্দ করে। ওদিকে উপদেশ হতে পারে আত্মহত্যা নিয়েও। সহজে আত্মহত্যার বিচিত্র উপায় বর্ণনা করা দ্য কমপ্লিট ম্যানুয়াল অব সুইসাইড নামের জাপানি বইটি ১৯৯৩ সালে জাপানে এক মিলিয়ন কপির ওপরে বিক্রি হয়েছিল। তবে বিক্রি যা–ই হোক, বহু সাহিত্য পুরস্কার চালু হওয়ার পরও আজ অব্দি যেকোনো ধরনের বইয়ের মান নির্ধারণের স্থির মানদণ্ড মেলে না। বই নিয়ে যদি যুক্তিযুক্ত সমালোচনার ঝড় ওঠে, তবে তা লেখকের উন্নয়ন ঘটায়। অন্য লেখকেরা তো করবেনই, যৌক্তিক সমালোচনা চাইলে একজন সাধারণ পাঠকও করতে পারেন। একবার হানড্রেড অর্থাস অ্যাগেইনস্ট আইনস্টাইন নামে একটি বই বেরিয়েছে শুনে আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘১০০ লেখকের প্রয়োজন পড়ল কেন, আমি যদি ভুল করে থাকি, তবে তা একজন বললেই যথেষ্ট।’
বইয়ের ভবিষ্যৎ
পৃথিবীময় বছরে ৯ লাখের বেশি বই প্রকাশিত হয় অথচ এখনো পৃথিবীর ১৫ শতাংশ মানুষ পড়তে-লিখতে জানে না। এত এত বই আর সাহিত্যের সঙ্গে তাদের এবং হয়তো আরও অনেকের কোনো সংশ্লিষ্টতা গড়ে ওঠে না। তবু বিভিন্ন উপলক্ষে বই প্রকাশের উৎসব নিরন্তর চলে। কাগজ আর বইয়ের ইতিহাসের পথ এখন আরও অনেক প্রশস্ত। ১৯৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসর আর ১৯৮৫ সালে সিডি আবিষ্কারের পর বই কম্পোজ আর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। এরপর দ্রুত ইন্টারনেটের আবির্ভাব, অনলাইনে বই বিক্রির ব্যবস্থা আর ২০০৭-এ ই-বুক রিডারের আবিষ্কার লেখক, প্রকাশক আর পাঠককে বইয়ের বাজার নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। অথচ এত কিছুর পরও মানুষ যা লেখে, তার সবটুকু কাগজে ছাপিয়ে ফেলতে চায়। কারও মনে থাকে না সাধারণ আকৃতির ৫০টা বই ছাপতে মাঝারি আকৃতির একটা গাছকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তবে সবকিছু হয়তো প্রকৃতিতেই ফিরে যায়, লাভ–ক্ষতিসহ ভিন্ন রূপে। বইয়ের পাতা যেমন পড়াও হয় আবার ঠোঙাও হয়। ষাট-সত্তরের দশকে জন্ম নেওয়া পাঠকের তারুণ্যে উত্তেজনা আনতে যে মিলস অ্যান্ড বুন প্রকাশনীর রোমান্টিক উপন্যাসের অবদান ছিল, লন্ডনের বার্মিংহামে হাইওয়ে রাস্তা বানাতে তার লাখ লাখ কপির মণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ কিংবা বই, প্রত্যেকেই তার অবধারিত পরিণতির দিকে ধাবিত। আবার অবিকৃত থাকলেও স্মৃতিময় সন্ধ্যার ওপরে সময়ের ধুলো জমার মতো বইয়ের গায়ে মেখে যায় পুরোনো গন্ধ। সে গন্ধ কেবল স্মৃতিজাগানিয়া নয়, বরং গন্ধ শুঁকে কোনো বিশেষজ্ঞ বলে দিতে পারেন বইটা কত বছর আগের। কাগজ আর কালির রাসায়নিক পরিবর্তন বছর বছর বইয়ের গন্ধকে বদলায়।
বিবলিওস্মিয়া নাকি সুন্ডোকু?
পুরোনো বইয়ের দোকানে কিছু মানুষ নেশাগ্রস্তের মতো ঘুরে ঘুরে হয়তো ছাইয়ের ভেতরে রত্ন খুঁজে পাওয়ার লোভে। বইপোকা ধরনের কারও কারও ওই গন্ধ ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না। পুরোনো বা পছন্দের বইয়ের গন্ধের প্রেমে পড়লে তাকে প্রেম বলে না, নাছোড়বান্দা রোগটিকে বলে বিবলিওস্মিয়া। চোখের সামনে বই মেলে রাখা ছাড়া এই রোগের চিকিৎসা নেই। মানুষের বেশি বেশি করে বিবলিওস্মিয়া হোক, তবে কখনো ‘সুন্ডোকু’ না হোক, চকচকে প্রচ্ছদ আর আপাত–আকর্ষণীয় তথ্যের লোভে শত শত বই কিনে স্তূপ গড়া কিন্তু কখনো না-পড়ার যে রোগের কথা জাপানিরা বলে।
তাই শুধু কেনা নয়, ক্রেতা বই পড়ে পাঠক হয়ে উঠুক।
এগারো শতকে দ্য টেল অব গেঞ্জি নামে একটি বই লিখেছিলেন মুরাসাকি শিকিবু। ৫৪ অধ্যায়ে লেখা জাপানি লেখিকার এই বইকে বলা হয় বিশ্বের প্রথম উপন্যাস।
এক হাজার বছর পর আজও সেই উপন্যাস মুগ্ধ হয়ে পড়ছেন পাঠক। মুঠোফোন বা ডিজিটাল স্ক্রিনে সব যখন দেখা যায়, হাতের নাগালে যখন লোভনীয় সব সিরিজ আর সিনেমা, তখনো কেন সেকেলে ভাষা ও ভঙ্গিতে লেখা হাজার বছরের পুরোনো এই উপন্যাস পড়ছেন মানুষ?
বই পড়ে মানুষ আসলে কী পান? জ্ঞান, আনন্দ আর তৃপ্তি তো পায়ই; পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক, উভয় স্বাস্থ্যেরই উপকার হয় বিস্তর। শৈশব থেকে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করে দেয় সারা জীবনের গভীর ভিত্তি। বই পড়ার আরও কিছু উপকারিতার কথা জানাচ্ছে হেলথলাইন ম্যাগাজিন।
শক্তিশালী হয় মস্তিষ্ক:
বই পড়ার অভ্যাসে আক্ষরিক অর্থে মন পরিবর্তন হয়। এমআরআই স্ক্যানার ব্যবহার করে গবেষকেরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পড়লে অনুরণিত হয় মস্তিষ্কের নিউরন। পড়ার ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিউরন নেটওয়ার্ক শক্তিশালী ও পরিশীলিত হয়। ২০১৩ সালের এক গবেষণা থেকে এসব তথ্য জানা যায়। গবেষকেরা মস্তিষ্কের প্রভাব জানতে উপন্যাস পড়ার সময় মানব মস্তিষ্কের এমআরআই স্ক্যান করেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা ৯ দিন ধরে পম্পেই নামের একটি উপন্যাস পড়েন। গল্পের উত্তেজনাকর নানান বিষয় পড়ার সময় মস্তিষ্কের নানান অংশে সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। মস্তিষ্কের স্ক্যান থেকে জানা যায়, বই পড়লে মস্তিষ্কের সংযোগ বৃদ্ধি পায়। সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সের অংশে পরিবর্তন দেখা যায়। মস্তিষ্কের এই অংশ চলাফেরা ও ব্যথার মতো শারীরিক সংবেদনে প্রতিক্রিয়া জানায়।
শিশুরা বদলে যায়:
যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের চিকিৎসকদের পরামর্শ, সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বই পড়ুন। শৈশব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় এমনটা করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। একই সঙ্গে বই পড়ার মাধ্যমে শিশু ও মা–বাবার মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। বাড়িতে পড়ার অভ্যাস থাকলে স্কুলে শিশুর পড়া ও অন্যান্য কর্মক্ষমতা বাড়ে। তৈরি হয় যোগাযোগ দক্ষতা, বাড়ে আত্মসম্মান। বই শিশুর মস্তিষ্ককে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করে।
বই পড়লে সহানুভূতি বাড়ে
গবেষণায় দেখা যায়, যাঁরা কথাসাহিত্য পড়েন, গল্পে থাকা বিভিন্ন চরিত্রের অভ্যন্তরীণ জীবনের খোঁজ রাখেন—অন্যদের অনুভূতি ও আবেগ তাঁরা বেশি বোঝেন। গবেষকেরা এই ক্ষমতাকে ‘থিওরি অব মাইন্ড’ (মনতত্ত্ব) বলেন। সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে, নিজেকে পরিচালনা করতে, সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সূত্র বইয়ের মধ্যে আছে। দীর্ঘমেয়াদি কথাসাহিত্য পড়ার অভ্যাস পাঠকের মনের জোর বাড়ায়।
শব্দভান্ডার তৈরি করে:
১৯৬০ দশকে বই পড়ার ওপর গবেষকেরা ‘ম্যাথিউ ইফেক্ট’ নামের একটি ধারণা নিয়ে আলোচনা করেন। যেসব শিক্ষার্থী নিয়মিত বই পড়েন, তাঁরা নিজের অজান্তে ছোটবেলা থেকে ধীরে ধীরে বড় শব্দভান্ডার তৈরি করেন। শব্দভান্ডারের পরিধি যাঁর যত ভালো, যত উন্নত হয়, তাঁর জীবনও তত উন্নত হওয়ার সুযোগ থাকে। নতুন শব্দ জানার ও চর্চা করার দারুন একটা উপায় হচ্ছে বই পড়া।
বয়স বাড়ার সংকট কমায়:
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনকে ব্যস্ত রাখার উপায় হিসেবে বই ও ম্যাগাজিন পড়ার পরামর্শ দিয়েছে। গবেষণার চূড়ান্ত প্রমাণ এখনো হাতে না এলেও আভাস মিলেছে, বই পড়ার অভ্যাস থাকলে আলঝেইমারের মতো রোগ প্রতিরোধ করা সহজ হয়ে যায়। বয়স্ক যাঁরা প্রতিদিন সুডোকু বা গণিতের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ঠিক থাকে, উন্নত হয়। তাই আপনি যত আগে পড়া শুরু করবেন, আপনার জন্য তত ভালো। যুক্তরাষ্ট্রের রাশ ইউনিভার্সিটির মেডিকেল সেন্টার ২০১৩ সালে একটি গবেষণা চালায়, যেখানে বলা হয়েছে, যাঁরা সারা জীবন বই পড়ার মতো কার্যকলাপে যুক্ত থাকেন, তাঁদের মস্তিষ্ক ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের চেয়ে ভালো থাকে। ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের চাপের স্তর জানতে যোগব্যায়াম, কৌতুক ও বই পড়ার প্রভাব পরিমাপ করা হয়। সেই সমীক্ষায় দেখা যায়, দিনে ৩০ মিনিট বই পড়লে রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন স্থির থাকে। মনস্তাত্ত্বিক সংকট কমে যায়।
জীবনমান উন্নত করে বই:
রাতে ঘুমানোর আগে চিকিৎসকেরা মুঠোফোনের পরিবর্তে ছাপা বই পড়তে পরামর্শ দেন। নিয়মিত বই পড়লে কমে আসে বিষণ্নতার উপসর্গ। বই পড়লে আয়ু বাড়ে, প্রায় ১২ বছর ধরে চলা এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়। ৩ হাজার ৬৩৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক অংশগ্রহণকারীর ওপর চালানো একটি জরিপে দেখা যায়, যাঁরা বই পড়েন, তাঁরা বই না–পড়ুয়াদের তুলনায় প্রায় দুই বছর বেশি বেঁচে থাকেন। যাঁরা প্রতি সপ্তাহে ৩০ মিনিট বই পড়েন, তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ২৩ শতাংশ বেশি।
সূত্র: হিস্ট্রি অব বুক, উইকিপিডিয়া, দ্য ইভল্যুশন অব বুক, জুলি ড্রিফাস, টেড-টক ইউটিউব ভিডিও, রিডিং ফর দ্য ফ্যানাটিকাল বুকওয়ার্ম, বুকস্টোর, ফ্যাক্টস অ্যাবাউট বুকস দ্যাট আর উইআরর্ডলি ইন্টারেস্টিং, হলোগিগলস, বে সাম, উইকিপিডিয়া। ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস অ্যাবাউট বুকস অ্যান্ড নভেলস, ফ্যাক্টস রিপাবলিক।

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান
ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com
মোবাইল +8801716599589
৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
© RP News 24.com 2013-2020
Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি
