সিলেট ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ | ১৪ই ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
প্রকাশিত: ৪:৪৮ পূর্বাহ্ণ, মে ৮, ২০২০

।। মারিয়ো বার্গাস ইয়োসা।। অনুবাদ: এহসানুল কবির।। রাস্তাটা খুব ছোট, দশ মিনিটে এ-মাথা ও-মাথা হেঁটে আসা যায়। লম্বায় ৪০০ গজের কম এই রাস্তাটা অক্সফোর্ড স্ট্রিট আর শাফ্ট্স্বুরি অ্যাভিনিউর 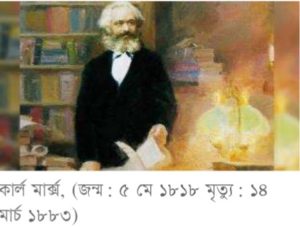
 মাঝ বরাবর চলে গেছে। লন্ডনের ফুর্তিভরা নিশিপাড়া সোহোর আর দশটা রাস্তার মতোই দেখতে: গাদাগাদি করে থাকা রেস্তোরাঁ, ক্লাব, শুঁড়িখানা, খাবারের দোকান, অলিগলি, পত্রিকা, পোস্টকার্ড আর রতিপুস্তক বিক্রির ঝুপড়ি, রাতের বেলায় সাদামাটা কাগজের ওপর ‘ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হয়’ কিংবা ‘লাস্যময়ী মডেল’ লেখা বিজ্ঞাপনশোভিত গণিকালয় আর ছোট ছোট ক্লাবঘরে ভরা, যেগুলোতে খরুচে আর বিবিক্ত পথচারীরা মাত্র ১০ শিলিঙে একটা বিবসনদৃশ্য বা রতিচিত্র দেখতে পারেন। জানালা আর জ্বলজ্বলে সাইনগুলোতে হাঙ্গেরি, ইতালি আর সিলন থেকে আসা বিচিত্র নামধারী খাবারের বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে। শুঁড়িখানাগুলো দেখতে অনেকটা সেঁ-জারমেইন-দে-প্রেসের ক্যাফেগুলোর মতো। একটার নাম লেজ আনফাঁ টেরিব্। সেখানকার সবজি ও ফলের দোকান, সেখানকার কড়া গন্ধ, সেখানকার আধা-গৃহী আধা-তন্দ্রাচ্ছন্ন খদ্দেরকুল—সব মিলিয়ে সোহোর অন্যান্য রাস্তার সেই জনপ্রিয়, উনিশ শতকি বখিল ভাবটা ডিন স্ট্রিটে নেই। ডিন স্ট্রিটে কোনো বাজার নেই; এর আমোদ-প্রমোদের উপকরণগুলো কারখানায় উৎপাদিত।
মাঝ বরাবর চলে গেছে। লন্ডনের ফুর্তিভরা নিশিপাড়া সোহোর আর দশটা রাস্তার মতোই দেখতে: গাদাগাদি করে থাকা রেস্তোরাঁ, ক্লাব, শুঁড়িখানা, খাবারের দোকান, অলিগলি, পত্রিকা, পোস্টকার্ড আর রতিপুস্তক বিক্রির ঝুপড়ি, রাতের বেলায় সাদামাটা কাগজের ওপর ‘ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হয়’ কিংবা ‘লাস্যময়ী মডেল’ লেখা বিজ্ঞাপনশোভিত গণিকালয় আর ছোট ছোট ক্লাবঘরে ভরা, যেগুলোতে খরুচে আর বিবিক্ত পথচারীরা মাত্র ১০ শিলিঙে একটা বিবসনদৃশ্য বা রতিচিত্র দেখতে পারেন। জানালা আর জ্বলজ্বলে সাইনগুলোতে হাঙ্গেরি, ইতালি আর সিলন থেকে আসা বিচিত্র নামধারী খাবারের বিজ্ঞাপন ভেসে ওঠে। শুঁড়িখানাগুলো দেখতে অনেকটা সেঁ-জারমেইন-দে-প্রেসের ক্যাফেগুলোর মতো। একটার নাম লেজ আনফাঁ টেরিব্। সেখানকার সবজি ও ফলের দোকান, সেখানকার কড়া গন্ধ, সেখানকার আধা-গৃহী আধা-তন্দ্রাচ্ছন্ন খদ্দেরকুল—সব মিলিয়ে সোহোর অন্যান্য রাস্তার সেই জনপ্রিয়, উনিশ শতকি বখিল ভাবটা ডিন স্ট্রিটে নেই। ডিন স্ট্রিটে কোনো বাজার নেই; এর আমোদ-প্রমোদের উপকরণগুলো কারখানায় উৎপাদিত।
যদিও ডিন স্ট্রিটের শুধু একটা কি দুইটা বাড়িকে দেখতে নতুন মনে হয় এবং বাকি সব কটি—তিন বা চারতলা পর্যন্ত উঁচু, একটা আরেকটার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো, কালের প্রলেপে যেগুলোর ইট কালো হয়ে গেছে—কমপক্ষে ১০০ বছরের পুরনো। এই ১০০ বছরে রাস্তাটার বাহ্যিক চেহারা নিশ্চয়ই অনেকখানি পাল্টে গেছে, কেননা, একে জীর্ণ কিংবা হতদরিদ্র মনে হয় না। ১৮৫৩ সালে (সেই সময়ের একটা পুলিশ-প্রতিবেদন অনুযায়ী) ডিন স্ট্রিট যে ‘লন্ডনের সবচেয়ে বাজে, সবচেয়ে সস্তা সড়ক’ ছিল, সেটা কল্পনা করা এখন কঠিন। আর এ-ও আন্দাজ করা শক্ত, ১৮৫০ সালে কেমন ছিল এই রাস্তাটার চেহারা, যখন দারিদ্র্যের চক্রে আটকা পড়ে মার্ক্স পরিবার এখানে বসবাস করতে আসেন, ছোট্ট দুইটা বসবাস-অনুপযোগী কামরায়, যেখানে তাঁরা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন, এক হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলো পার করবেন। যে বাসায় তাঁরা থাকতেন, তাতে কোনো নামফলক নেই এবং জীবনীগ্রন্থগুলোতে যে আদি নম্বরটি পাওয়া যায়, তা এর মধ্যে বদলে গেছে বলে অনুসন্ধিৎসু বা পূজারীস্বভাবের লোকজনকে মার্ক্স স্মৃতি গ্রন্থাগারে যেতে হয় উভয় পাশে গলিবেষ্টিত শান্ত এই বাসাটার সেই কামরার জানালাদুটোর হদিস জানতে, যেটা ছিল মার্ক্সের বাচ্চাদের বসার, খাওয়ার, পড়ার, শোবার ঘর (ভিতরের কামরাটা ছিল মা-বাবার শোবার ঘর)।
কার্ল মার্ক্স, লন্ডন
কার্ল মার্ক্স, লন্ডন
শীতকাল এসে গেছে, বাইরে খুব বেশিক্ষণ থাকলে ঠান্ডায় নাক-কান জমে যায় আর হাত দুটো হয়ে পড়ে অসাড়, তাই আমি ছোট্ট, ধোঁয়াচ্ছন্ন, জনাকীর্ণ একটা শুঁড়িখানায় সেঁধোলাম, যেটাতে কিনা কফি বিক্রি হয় না। অগত্যা এক গ্লাস উষ্ণ বিলাতি বিয়ার চাইতে হল। তবে কপাল ভালো যে রেডিয়েটরের পাশেই একটা খালি আসন পেয়েছি, যেখান থেকে সোজা ওই ছোট্ট জানালা দুটো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই ডিন স্ট্রিটে কী উদ্ধার করছি আমি! পরিতাপের বিষয়, সম্প্রতি যে বই দুটো পড়ছিলাম, সেগুলোও সঙ্গে আনিনি; তা নাহলে বইদুটোর যে পাতাগুলোতে মার্ক্সের ডিন স্ট্রিটে কাটানো জীবনের কথা আছে, সেগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারতাম, আমার বিস্ময় ও মুগ্ধ ভক্তিকে আরও একবার উসকে দিয়ে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তাগণের লেখাপত্র ফ্রান্জ্ মেরিংয়ের করা জীবনীগ্রন্থকে ছাপিয়ে গেছে এবং সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে এডমন্ড উইল্সনের প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকেই বিতর্কযোগ্য, কিন্তু মার্ক্সের জীবনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়, ডিন স্ট্রিটের বিস্ময়কর ও ভয়াবহ ছয় বছর সম্পর্কে এই দুই বইয়ে যে ছবিটা পাওয়া যায়, সেটা এর চেয়ে ভালোভাবে আঁকা প্রায় অসম্ভব। উভয় গ্রন্থেই আছে মহাকাব্যিক দ্যোতনাদায়ী একটা ছবি, সমাজের বিরুদ্ধে, অশুভর বিরুদ্ধে একক যুদ্ধে বিজয়ী নায়কের জয়গাথা, যা ধ্রুপদী কাব্য ও কাহিনিতে প্রায়ই পাওয়া যায়। হতাশ লাগছে; তাড়াহুড়া করে, অনেক উৎকণ্ঠা নিয়ে এখানে এসেছি আমি, সেই অবিস্মরণীয় যুদ্ধের কিছু অবশেষ আর স্মৃতিচিহ্ন খুঁজতে, কিন্তু শেষমেশ আবিষ্কার করলাম, সেই যুদ্ধটা যেখানে হয়েছিল সেটা এখন একটা কৃত্রিম, অভিজাত এলাকা, যেখানে স্থানীয় বুর্জোয়া আর মালদার পর্যটকেরা আসেন রসনাবিলাস করতে, মদ খেতে আর সেক্স কিনতে। এটা অস্বস্তিকর ও বৈপরীত্যময় যে এই এলাকা, এই রাস্তা—এক অর্থে যেখানে বুর্জোয়াদের সবচেয়ে মারকুটে এবং সফলকাম প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম হয়েছিল—এখন বুর্জোয়াদের ফূর্তির জন্য লন্ডনের সবচেয়ে নষ্ট ও অবক্ষয়িত অঞ্চল। নিঃসন্দেহে বলতে পারি, মার্ক্সের সময় ডিন স্ট্রিটে কোনো বুর্জোয়ার পা পড়েনি।
লন্ডনে আসার আগের কয়েক মাসে মার্ক্স পরিবারের ওপর নেমে এসেছিল সব ধরনের দুর্গতি। জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাঁরা ব্রাসেল্সের শ্রমিক-অধ্যুষিত এক শহরতলিতে আশ্রয় নেন, এরপর একদিন মার্ক্স পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ফ্রান্সে নির্বাসিত হন। মার্ক্সকে খুঁজতে বের হলে জেনি মার্ক্স ফ্রান্সের পুলিশবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত ও ভবঘুরেপনার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দী হন এবং এক বারবণিতার সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতে বাধ্য হন। প্যারিসে ছদ্মনামে বসবাস করা সত্ত্বেও মার্ক্স পরিবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং ইংল্যান্ডে প্রেরিত হয়। তবে তখনো তাঁদের হাতে কিছু টাকা ছিল এবং ক্যাম্বরওয়েলে একটি সুসজ্জিত ঘর ভাড়া নিয়ে লন্ডনে প্রথম কয়েক মাস তাঁরা কিছুটা স্বচ্ছন্দে কাটান। ১৮৫০ সালে সেই টাকা শেষ হয়ে যায় এবং বাড়িওয়ালা তাঁদেরকে বের করে দেন। এরপর তাঁরা এখানে চলে আসেন এবং ক্রমে পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি হয়। স্থানীয় দোকানগুলোতে খাবারের বিল দিতে পারেননি বলে তাঁদের আসবাব, বিছানাপত্র, খেলনাপাতিসহ ঘরের প্রায় সব জিনিস জব্দ ও বিক্রি করে দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক মাস বয়সী সবচেয়ে ছোট ছেলেটা, এসব নিগ্রহ ও নির্বাসনের ভেতরে যার জন্ম, অসুস্থ হয়ে পড়ে; প্রয়োজনীয় শুশ্রূষা ও খাবারের অভাবে সে মারা যায়। মাসের পর মাস মার্ক্স পরিবার শুধু আলু আর পাউরুটি খেয়েই জীবনধারণ করে, এবং প্রথম শীতে মা-বাবা ও বাচ্চাদের ফ্লু হয়। সবচেয়ে ছোট মেয়েটা টিকে থাকতে না পেরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা পড়ে। প্রায় একই সময়ে সোহোতে কলেরার মহামারি দেখা দেয় এবং অধিকাংশ লোক এলাকা ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু টাকার অভাবে মার্ক্সদের থেকে যেতে হয়। তাঁদের পোশাক-আশাকসহ (বাচ্চাদের জুতা আর মার্ক্সের ওভারকোট বিক্রি করে দেওয়া হয়) যৎসামান্য জিনিসপত্র যা বাকি ছিল, পরের বছর তা-ও জব্দ হয়। এক রাতে বাসায় পুলিশ আসে এবং চুরির অপরাধে মার্ক্সকে আটক করে: ডিন স্ট্রিটের এক প্রতিবেশীর সন্দেহ হয় যে মার্ক্সদের একটা কামরায় কাচের যে অলংকারটা শোভা পাচ্ছিল (পরিবারের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, যা জেনি আগলে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন), সেটা চুরির মাল। ১৮৫৫ সালে বাকি ছেলেটাও মারা যায় এবং ওই ছয় বছরের অজস্র দুর্বিপাকের মধ্যে মনে হয় এটাই মার্ক্সকে সবচেয়ে গভীরভাবে আহত করেছিল। ‘সব ধরনের দুর্ভোগ আমি পুইয়েছি,’ এঙ্গেল্সের কাছে মার্ক্স লিখেছিলেন, ‘কিন্তু এখন, এই প্রথমবারের মতো, আমি বুঝতে পারছি দুর্বিপাক কাকে বলে।’ এখানে, এই ডিন স্ট্রিটে মার্ক্সরা যখন চূড়ান্ত দারিদ্র্যে নিপতিত, তখন এঙ্গেল্স্ ম্যানচেস্টারের ঘৃণিত পারিবারিক শিল্পকারখানায় যোগ দেওয়ার বীরোচিত সিদ্ধান্ত নেন, যেন তিনি মার্ক্সকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারেন। নিউইয়র্কের ‘দ্য নিউইয়র্ক টাইমস’ ও ‘নিউইয়র্ক ট্রিবিউন’ পত্রিকায়, মার্ক্স যে প্রবন্ধগুলো পাঠান, যেগুলো দিয়ে পরিবারটির রুটি-রুজির সংস্থান হয়, সে প্রবন্ধগুলো মার্ক্সের নামে লিখতে রাজি হয়েছিলেন এঙ্গেল্স্, যেন মার্ক্স তাঁর অর্থনীতি পড়া নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারেন। এখানে, এই ডিন স্ট্রিটেই, মার্ক্সের জীবনযাত্রার তদন্ত করতে এসেছিলেন পুলিশের একজন এবং ১৮৫৩ সালে লেখা তাঁর প্রতিবেদনটা একটা মূল্যবান দলিল:
দুটো কামরার কোনোটিতেই কোনো পরিষ্কার বা ভদ্রোচিত আসবাব নেই, প্রতিটা জিনিস জীর্ণ আর ছেঁড়া, সবকিছুর ওপরে ধুলার পুরু স্তর…ডাঁই করে রাখা বাচ্চাদের খেলনাপাতি, স্ত্রীর শেলাইবাক্সের টুকরো-টাকরা, কানাভাঙা কাপ, ময়লা চামচ, ছুরি, কাঁটাচামচ, কুপিবাতি, একটা দোয়াত, পেয়ালা, হল্যান্ডে তৈরি কয়েকটা মাটির পাইপ, তামাকের ছাই—এসব ছাড়াও পাণ্ডুলিপি, বই ও পত্রিকা…মার্ক্সের কামরায় ঢোকামাত্র তামাকের ধোঁয়ায় চোখে এমনভাবে পানি আসবে…যেন একটা গুহার ভেতরে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আপনি…বসার ব্যাপারটাও খুব বিপজ্জনক। এদিকে তিন পা-ওয়ালা একটা চেয়ার আছে, ওদিকে আরেকটা আছে আস্ত, যেটাতে বাচ্চারা রান্নাবাটি খেলছে।
এবং সেই একই বিবেকবান পুলিশ আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, ‘স্বামী ও পিতা হিসাবে, তাঁর অস্থির ও খ্যাপাটে স্বভাব সত্ত্বেও, [মার্ক্স] চূড়ান্তরকম নম্র ও ভদ্র।’
মেয়ের সঙ্গে মার্ক্স
মেয়ের সঙ্গে মার্ক্স
এখানে, এই ডিন স্ট্রিটে, মার্ক্সের রাজনৈতিক তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড অতিমানবিক শক্তি ও বলবত্তা অর্জন করে। এখানেই তিনি সকল দুর্ভোগ, পারিবারিক ট্রাজেডি আর অসুস্থতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দৈনিক আট ঘণ্টা পড়বেন বলে ঠিক করেন এবং কঠোরভাবে তা অনুসরণ করেন। তাঁর দিনানুদিনের অভিযানটা কল্পনা করা খুব একটা কঠিন নয়, সকাল নয়টায় বেরিয়ে পড়া আর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফিরে আসা, এরপর আরও তিন কি চার ঘণ্টা (যা আবার কখনো পাঁচ বা ততোধিকে গড়াত) পড়া নিজের কামরায় বসে, ওখানটায়, ওই জানালা দুটোর ওপাশে। এখানেই, সেই মহামারির সময়, ‘ফ্রান্সের শ্রেণিসংগ্রাম’ শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধটা শেষ করেন এবং পরের বছর, বাচ্চাকাচ্চারা যখন চাবুক হাতে নিয়ে টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে হ্রেষাধ্বনি করছিল, তিনি লেখেন ‘লুই বোনাপার্তের অষ্টাদশ ব্রুমের’। এখানে বসেই তিনি ‘দাস ক্যাপিটাল’ বইয়ের জন্য প্রথম কয়েক খাতা নোট লেখেন এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে এঙ্গেল্সের সঙ্গে আলোচনা করেন প্রাত্যহিক দীর্ঘ পত্রমালার মারফত। এখানে, সেই ছয় বছরে, তিনি নানান ভাষা শেখেন, পাঠাগারের গোটা গোটা বিভাগ সাবাড় করেন, শত শত প্রবন্ধ লেখেন আর এত সবের মধ্যেই সময় বের করে নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা গল্প বোনেন হান্স রকল নামের এক কাল্পনিক চরিত্র নিয়ে’ ‘যে একটা জাদুর দোকানের মালিক ছিল কিন্তু যার পকেটে কখনো একটা পয়সাও থাকত না।’
এ রকম ভীষণ বৈরী পরিবেশে এ বিরাট ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাবার উদ্যম আর শক্তি তিনি পেয়েছিলেন কোথা থেকে, কীভাবে? এডমুন্ড উইলসনের লেখা বইটাতে মার্ক্সের একটা উদ্ধৃতি আছে, যেটা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ওটা সেই সময়ের লেখা, যখনও তিনি একটা ঝগড়াটে ছাত্র, ভীষণ পরিহাসপ্রবণ আর প্রতিভাধর, যখন তিনি হেগেল পড়ছিলেন গভীর অনুরাগে আর জেনিকে লিখে পাঠাচ্ছিলেন দিলদিওয়ানা প্রেমের কবিতা। ‘একজন লেখক’, তিনি বলেন, ‘জীবিকা নির্বাহ করার ও লেখার জন্য টাকা কামাতে পারেন, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই টাকা কামানোর জন্য জীবিকা নির্বাহ করা বা লেখা তার উচিত নয়। লেখার কাজটাকে কোনো অবস্থাতেই উপার্জনের অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। লেখকের কাছে লেখার কাজটা আপনাতেই সমাপ্ত একটা প্রক্রিয়া; এবং এটা তার কাছে অতি অবশ্যই কোনো অবলম্বন নয়, কেননা, লেখার জন্য লেখক প্রয়োজনে নিজের অস্তিত্বকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকেন। ধর্মের ক্ষেত্রে যাজক যেমনটা করেন, মানুষের সঙ্গে—যাদের মধ্যে তিনিও মানুষী চাহিদা ও চাওয়া-পাওয়ায় বন্দী—বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে লেখকও অনেকটা তেমনিভাবেই আঁকড়ে রাখেন “বান্দার আগে আল্লাহর অনুগত হও” এই মূলমন্ত্র।’
এই অনুচ্ছেদটা আমি কয়েকবার করে পড়েছি; এখন, লম্বা কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, দরজিবাড়িতে বানানো স্যুট, নীল-গোলাপি জামা, ফুলেল টাই আর আলখাল্লা পরা তরুণ-তরুণীতে গিজগিজ করা—বিশুদ্ধতাবাদী লন্ডনে এখন যা ঘটছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে ‘অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিশোধ’—এই পানশালায় বসে সেই উদ্ধৃতিটার কথা খুব মনে পড়ছে। ফ্লবেয়ার কি ওই একই লেখায় স্বাক্ষর করতেন না, একটা কমাও না পাল্টে? অসম্ভব ক্ষমতাধর ও অধ্যবসায়ী ফ্লবেয়ার, ক্রোয়াসের সেই নিঃসঙ্গ মানুষটা কি স্রষ্টা আর তাঁর কাজের সংজ্ঞার্থ প্রায় একইভাবেই নিরুপণ করেননি?
ডিন স্ট্রিটে আঁধার নেমে এসেছে, আর আজকে শনিবার বলে প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে লোকজন ফুটপাথের এ-মাথা ও-মাথা হাঁটছে, ধীরে ও অনুসন্ধিৎসুভাবে, বিচিত্র রেস্তোরাঁগুলোর জানালা, রতিপুস্তকের ঝুপড়ি, ছদ্মবেশী গণিকালয়, প্রেক্ষাঘর ও বিবসনগৃহের ওপর চোখ বোলাচ্ছে। ওই জুড়ি-জানালার সামনে এসে আমি থেমেছি আর সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন কি চারজন পথচারী থামে এবং উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়: কোন বীভৎস দৃশ্য দেখতে চাইছিল তারা সেখানে? কিন্তু ঘরটার দরজা-জানালা বন্ধ, তাই হতাশ হয়ে তারা সটকে পড়ে। আমিও চলে আসি এবং ডিন স্ট্রিটে মার্ক্সের নিবাসের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য কেউ যে ওখানে কোনো ফলক বসানোর কথা ভাবেনি, তা নিয়ে আমার আর কোনো অনুশোচনা থাকে না।
লন্ডন, নভেম্বর ১৯৬৬

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান
ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com
মোবাইল +8801716599589
৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
© RP News 24.com 2013-2020
Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি
