সিলেট ১৪ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ২৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
প্রকাশিত: ৩:২২ পূর্বাহ্ণ, জুন ৩০, ২০২০
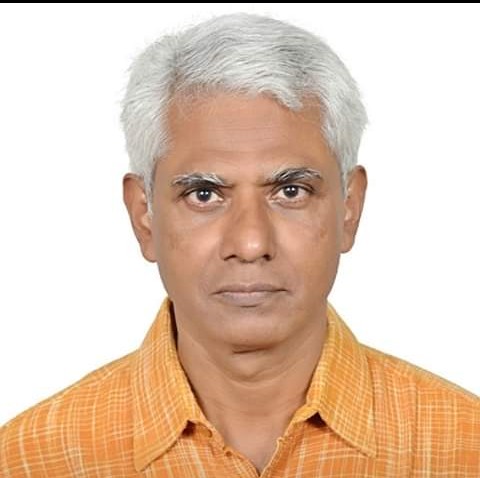
|| রাহমান চৌধুরী || ৩০ জুন ২০২০ : বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে আশির দশকের শেষের দিকের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক ছিল সাতঘাটের কানাকড়ি। মহিলা সমিতি মিলনায়তনের দ্বিতীয় সারিতে বসে নাটকটি দেখছিলাম। সামনের সারিতে ঠিক আমার সামনে বসেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আমার শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যিনি পরবর্তীতে বাংলাপিডিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা আর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। সিরাজুল ইসলাম সেদিন ছিলেন নাট্যকারের আমন্ত্রিত অতিথি। নাটকটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল, বহুজন প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কিন্তু সেদিন আমি নাটকটা বিরতি পর্যন্ত দেখে বের হয়ে যাই। সিরাজ স্যার নাটক দেখার পর আমাকে খুঁজে পাননি। নিজেই পরদিন সেটা ফোনে জানালেন আমাকে। বললাম, স্যার এরকম অরুচিকর নাটক দেখতে আমি অভ্যেস্ত নই। ফলে নাটকটা পুরো না দেখে এবং আপনার সঙ্গে দেখা না করে চলে আসি। স্যার বললেন, নাটকটা নিয়ে আমার অনেক বক্তব্য আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসো, চা খাই একসঙ্গে। চা খাওয়া মানে, নাটকটা নিয়ে স্যারের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। স্যার নিজে নাটকটা দেখে খুব হতাশ কিন্তু আমন্ত্রিত ছিলেন বলে সবটা না দেখে চলে আসতে পারেননি। কয়েকবারই পিছনে ফিরে নাকি আমাকে খুঁজে ছিলেন। স্যার সেদিন নাটক দেখার পর সংস্কৃতি জগতের অবনতি দেখে খুব দুঃখ করেছিলেন। স্যার খুব একটা নাটক দেখতেন না বা সাহিত্য পড়তেন না। কারণ ইতিহাসের গবেষণা বা লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু যা পড়তেন বা যা দেখতেন সেসব সমাজবিজ্ঞানে দৃষ্টিতে চমৎকার মন্তব্য করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন, নাটক-সাহিত্য শুধু সমাজের মঙ্গল করে না, কখনো কখনো খুব ক্ষতি করে। নাটক আর সাহিত্যের ভাষা যদি কদর্য হয়, সমাজের রুচির বিকৃতি ঘটায়। স্যার আরো বললেন, যখন নাটকটা না দেখে তুমি রাগ করে চলে এসেছো, তখন আমি দেখছি পুরো মিলনায়তন দর্শকের হাতিতালিতে মুখরিত। স্যার পরে আরো অনেক কথা বলেছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন, মাথা গরম করে শিল্পসাহিত্য নাটক রচনা করলে, সমাজ বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নাটক দেখতে গিয়ে যদি কিছু সংলাপ দ্বারা মুগ্ধ হতে না পারলাম, চরিত্ররা যদি চিন্তার খোরাক না জোগালো, পুরো আখ্যানের মধ্যে সঙ্গতি না থাকলো; কী হলো সেটা!
সাতঘাটের কানাকড়ি নাটকটা যেমাথা গরম করে লেখা, নাট্যকার নিজেই তা স্বীকার করেছেন। নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় লিখছেন, ‘কিছু দর্শক আমি পেয়েছি যাঁরা এ নাটক দেখে অ-খুশী হয়েছেন। তাদের মতে সাতঘাটের কানাকড়ি শিল্পসম্মত সাহিত্য হয়নি।…না, আমি শিল্পকর্মের সূক্ষ্ম ও সচেতন অভিলাষ নিয়ে সাতঘাটের কানাকড়ি রচনা বা নির্দেশনা করিনি। সাতঘাটের কানাকড়ি নাটকটি রচনার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আমার কালের দগ্ধীভূত উত্তপ্ত কথাগুলো বলা এবং কালের মানুষের ক্রোধ ও দহনকে প্রকাশ করা। মমতাজউদ্দীন আহমদ নিজেই স্বীকার করছেন তিনি ক্রোধ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বহু বছর পর যখন সিরাজ স্যারের সঙ্গে আমার পিএইচডি করা রাজনৈতিক নাটক নিয়ে, গবেষণার প্রয়োজনে বাধ্য হলাম তখন সাতঘাটের কানাকড়ি পাঠ করতে। পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাটকের কয়েকটা সংলাপ এখানে লিখছি। নটিকের চরিত্রদের সংলাপ, নায়ক বলছে নায়িকাকে, ‘যদি তোমাকে ছায়াছবির খচ্চর মার্কা নায়িকার মতো অর্ধ উলঙ্গ করে দেই’। ‘তুমি ন্যাংটা হয়ে নাচবে আমি ষাড়ের মতো ফাল দেব।’ ভিন্ন একটি সংলাপ, ‘শালার বউটা মোটা হয়েই যাচ্ছে। চর্বির গোডাউন। পাঁচশো লোককে ঐ চর্বি দিয়ে পরোটা ভেজে খাওয়ানো যাবে।’ নাটকটা নাকি লেখা সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে। সামরিক স্বৈরশাসনের সঙ্গে রগরগে এসব সংলাপের সম্পর্কটা কী? রুচির বিকৃতি ছাড়া কী আছে আর এসব সংলাপে। শুধু ‘সাতঘাটের কানাকড়ি’ নয়, বহু নাটকে মাঝে মধ্যে এইরকম রগরগে সংলাপ শোনা গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত কিছু ব্যক্তি সাতঘাটের কানাকড়ি নাটক সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও নাট্যাঙ্গনের বহু লোক নাটকটিকে উচ্চ মূল্য দেননি। যেমন আতাউর রহমান লিখছেন, ‘নিছক দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটকটির ভাল দিক খুঁজতে লাগলাম কিন্তু খুঁজে প্রায় কিছুই পেলাম না। নাটকের কাহিনী বক্তব্যের উপস্থাপনা, অভিনয় কোনোটির সাথেই মন সায় দিল না, তবুও নিবিষ্ট হয়ে মনের গভীরে সন্ধান চালালাম, প্রাপ্তি অকিঞ্চিতকরতায় নিরাশ হলাম, এতে আরও বিপদগ্রস্ত বোধ করলাম, কারণ প্রযোজনাটি ভীষণ জনপ্রিয়। এই সূত্র ধরে নাটকটির জনপ্রিয়তার প্রশ্নে মনে ধন্ধও লাগল।’
যখন আমি “রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক” শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লিখি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাট্যচর্চার নানা অশ্লীলতা নিয়ে মন্তব্য করেছিলাম। পরবর্তীতে দুহাজার পাঁচ সালে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় “বাংলাদেশের নাটকে হাসি এবং অশ্লীলতা” নামে একটি গবেষণামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম। নাটকে যদি নাট্যকার রাগে ক্ষোভে যা খুশি ভাষা ব্যবহার করতে পারেন শাসকদের সমালোচনার নামে, সাধারণ মানুষ তাহলে যদি কাউকে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে তেমন ভাষা ব্যবহার করেন, সত্যিই কি দোষ দেয়া যায়? সংস্কৃতি চর্চার ভিতর দিয়ে রুচি গড়ে তোলবার কথা যাদের, যদি কুরুচিপূর্ণ ভাষা তাঁরা নিজেরাই খুব সচেতনভাবে গর্ব নিয়ে ব্যবহার করেন, তাহলে বাকিদের কাছ থেকে ভিন্ন কিছু কী করে আশা করি? বিষবৃক্ষ রোপন করলে ফল তো ভোগ করতেই হবে। দুর্ভাগ্য হচ্ছে এইযে, বিষবৃক্ষটি সকলে রোপন করে না, রোপন করে কতিপয় মানুষ কিন্তু দিনের শেষে তার পরিণতি ভোগ করতে হয় পুরো সমাজকে। রিজওয়ানা চৌধুরীর ক্ষেত্রে যা ঘটে গেছে তা বহু পূর্বে নানাভাবে চাষকরা বিষবৃক্ষের পরিণাম। কয়েকদিন আগে দেখলাম রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার প্রতি আক্রমণ নিয়ে একজন লিখেছেন, মাদ্রাসার আর নিম্নবর্গের ভাষাটা এমনই হয়। তিনি যা বলতে চান তার সার কথাটা হলো, কিছুলোক ভদ্রলোক থাকবেন আর ভোগবিলাসিতা করবেন, বিশ্ববিদ্যালয় পড়বেন, বাকিদের রাখবেন দরিদ্র বানিয়ে। মাদ্রাসায় পড়া আর দরিদ্র মানুষের ভাষা তো এমনটা হবেই। মূল কথাটা হলো কিছু মানুষকে নিষ্পেষণ করে, সুন্দর ভদ্র সমাজ বানানো যায় না। কথাটার মধ্যে যুক্তি রয়েছে। কথাটা বিরাট কিছু প্রশ্নকে সামনে এনেছে। নিশ্চয় তার জন্য বক্তার ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। বক্তা হয়তো সেদিকটাতে নজর দেননি। সবসময় আমরা মনে করি কুরুচিপূর্ণ ভাষাটা বুঝি বস্তির ভাষা। কিন্তু ধারণাটা ভুল।
যতো দোষ নন্দ ঘোষের মতো মাদ্রাসা আর মৌলবাদকে আক্রমণ করাটা একটা রোগে পরিণত হয়েছে। ভাবখানা, সব অপকর্ম করে মৌলবাদীরা আর বাকিরা সব পুতপবিত্র। সব বাদ দিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করি, স্বাস্থ্যসেবা খাতে যে দুর্নীতিটা হচ্ছে, সেটার সঙ্গে কি মৌলবাদীরা জড়িত? ব্যাংকের লুটপাটের সঙ্গে জড়িত কারা? মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পায় না সেটা খুব সত্যি কথা। কিন্তু শততম ধর্ষণের উৎসবটা পালিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিনাবিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্ররোচনায় সেই ধর্ষক বিদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। যদি শিক্ষকদের একজনের নাম বলি বহুজন চমকে উঠবেন। মনে হলো অনেকের লেখা পড়ে, মাদ্রাসার সবাই অশ্লীল কথা বলে আর বাকিরা সব শ্লীল কথা বলেন। ভদ্রসমাজে কি অশ্লীল গালাগালি নাই? বন্যাকে নিয়ে যারা কুরুচিকর মন্তব্য করেছে সবাই কি মাদ্রাসার, না কি সবাই নিম্নবর্গের? বিশ্বে পর্ণ বানায় কি মাদ্রাসার লোকরা? চলচ্চিত্র, নাটক, সাহিত্যে বিভিন্নভাবে যে অশ্লীলতার আমদানি করা হয়, সেটা কি মাদ্রাসার নির্মিত, না কি দরিদ্রদের নির্মিত? কারা বানায় সেগুলি? ধনীক শ্রেণী। কিছু দরিদ্র মানুষ বাঁচার সংগ্রামে তার সঙ্গে যুক্ত হন। সাতঘাটের কানাকড়ি কাদের হাতে নির্মিত? তিনি স্বনামধন্য একজন অধ্যাপক। বর্তমান সময়ে ফেসবুকে বহুজনের লেখায় প্রায় দেখা যায়, নানারকম অশ্লীল শব্দ, খিস্তি। যথেষ্ট তথাকথিত প্রগতিশীলদের কলম থেকেও সেটা বের হয়। বহুজন মনে করেন সেটাই নাকি স্মার্ট হবার লক্ষণ। প্রথাভাঙ্গার পথ। রামমোহন, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়াকে প্রথা ভাঙ্গার জন্য খিস্তি করতে হয়নি। কিন্তু শত বছর এগিয়ে নিয়ে গেছে সমাজকে। যারা নিজেরা খিস্তি করে আর সাহিত্যে অশ্লীলতা আমদানি করে বাহবা পেতে চান, মনে রাখতে হবে সেটা নতুন কিছু নয়। বাংলার নবজাগরণের কালে আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতায় তার দেখা মেলেছে বহুক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি, কাব্যে। কিন্তু সেসবের গভীরতার যে দিকটি ছিল, মাটির যে ঘ্রাণ ছিল তা ভদ্রলোকি অশ্লীলতায় নেই। কিন্তু কলকাতার সেই আদিরসাত্মক শিল্প-সংস্কৃতি সেটা খুব বেশিদিন চলেনি। বটতলার সাহিত্য খুঁজলে তা এখনো পাওয়া যাবে। বটতলার সাহিত্যের অাছে এক বিরাট দিগন্ত।
ইশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল সাহিত্যের জগতে যে জোয়ার এনেছিলেন তার স্রোতে তা ভেসে যায়। পরবর্তীতে শরৎচন্দ্র, বিভুতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর সাহিত্যে বহুকিছু এনেছেন, জীবনের সবদিককে ধারণ করেছেন কিন্তু ভাষাকে তার জন্য নিম্নরুচির করতে হয়নি। যারা পরবর্তীযুগে ভাষাকে নিম্নরুচির করেছেন, তাদের কেউ উল্লেখিতদের রচনার মানকে ছাড়াতে পারেননি। যুদ্ধে বহু কিছু ঘটে; হত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার, বন্দীদশা। যদি কেউ মনে করেন, তিনি ধর্ষণটাকে রগরগে করে দেখাবেন, হ্যাঁ, তাতে বাণিজ্য হতে পারে; যুদ্ধের গভীরতা বা ঘৃণার প্রকাশ তাতে থাকে না। ঢাকার মঞ্চে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম একবার এক নাট্যকার-নির্দেশকের অনুরোধে। নাটকটাতে ধর্ষণের দৃশ্য ছিল। পুলিশ বিদ্রোহীদের দমন করতে গ্রামে এসে দলগতভাবে তাদের নারীদের ধর্ষণ করছে। ঠিক আছে, ধর্ষণ দেখানো যেতেই পারে। কিন্তু দেখা গেল, ধর্ষণের দৃশ্যটি যখন চলছে, দর্শকরা হা হা করে হাসছে। ধর্ষণের দৃশ্যে মানুষের কষ্ট পাবার কথা, ক্রুদ্ধ হবার কথা, ঘৃণা জাগবার কথা ধর্ষকের প্রতি। কিন্তু দর্শক মজা পেয়ে হাসছে। নাট্যকার-নির্দেশক যখন নাটক শেষে কথা বলতে এলেন। বললাম তাঁকে কথাটা। তিনি আমাদের বর্তমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আর মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর মতো নিজের ত্রুটি স্বীকার না করে বলে বসলেন, না এর মধ্যে ত্রুটির কিছু নেই। ধরে নেন, আমি চেয়েছি দৃশ্যটাতে দর্শককে হাসাতে। চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আর কী করার থাকে। কিন্তু এঁরাই এখন নাট্য জগতের মহীরুহ। খুব নামকরা একজনের নাটকে এরকম দেখেছি আগে। দেখেছি চলচ্চিত্রে। মনে হচ্ছে, ধর্ষণ যেন একটা আনন্দের ব্যাপার, দর্শকদের তাতে খুশি হবার কথা। যখন এরশাদের সামরিক শাসন চলছে, বহু পথ নাটকে দেখেছি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে এরশাদ, এরশাদের স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ সংলাপ বলা হয়েছে। কিন্তু তাতে রাজনীতি বা গণতন্ত্রের কী লাভ হয়েছে? ক্ষমতা ছেড়ে এরশাদ আবার ক্ষমতাবান হয়েছেন ভিন্নভাবে। মারা যাবার পর সম্মানের সঙ্গে সমাধি লাভ করেছেন। কিছু নাটক ইতিবাচক ভূমিকা রাখলেও, কুরুচিপূর্ণ নাটকগুলি আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেগুলি না দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হবে, না নিজ সময়ের দাবি মেটাতে পেরেছে। কুরুচিপূর্ণ নাটকগুলি না গণতন্ত্র চালু করতে পেরেছে, না লুটপাট বন্ধে কাজে এসেছে। কুরুচিপূর্ণ এসব লেখা মহত্তর কাজে আসে না বরং সমাজকে কলুসিত করে। চারদিকে তাকালে ভয়াবহ সব প্রমাণ পাওয়া যাবে।
ফলে মনে রাখতে হবে, যা কিছু ঘটে হঠাৎ রাতারাতি ঘটে না। বহুদিন ধরেই ঘটছে, ঘটার রাস্তা নিজেরাই আমরা তৈরি করে রেখেছি। যখন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে তখন আমরা চেঁচামেচি করতে বাধ্য হই। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটা লেখা লিখেছিলেন “শাড়ি” নিয়ে। সেই লেখাটার সমালোচনা হতেই পারে, দ্বিমত করা যেতে পারে। কিন্তু সমালোচনার চেয়ে আক্রমণ হলো বেশি। সায়ীদ সাহেবকে লক্ষ্য করে নাট্যজগতের একজন ফেসবুকে বললেন, হ্যাঁ আমি শাড়ি পড়েছি, আমার শরীরের ভাঁজ দেখুন। শাড়ি নিয়ে লেখাটার চেয়ে ব্যক্তিগত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আক্রমণের শিকার হলেন বেশি। বলা যায় হেনস্থা করা হলো তাঁকে। সাধারণ মানুষরা তা করেননি। করেছেন সংস্কৃতি জগতের, নাট্য জগতের, শিক্ষিত ভদ্রজগতের মহারথীরা। খুব দুঃখজনক ঘটনা ছিল সেটা। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটাও দুঃখজনক। কিন্তু এরকম ঘটাবার পথ তো আগেই তৈরি করা আছে। সম্মান কী বস্তু যেন আমরা ভুলতে চাইছি। হয় ব্যক্তি পূজা, নাহলে ব্যক্তিঘৃণা। মাঝামাঝি কোনো জায়গা নেই। যদি গত ত্রিশ বছরের জাতীয় সংসদের দিকে তাকানো যায়, বুঝতে পারবো মানুষকে সম্মান করার সংস্কৃতিটা কবে থেকেই নিম্নগামী হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে পরস্পরকে অাক্রমণের ভাষাটা বহুদিন ধরেই সুস্থতার চিহ্ন বহন করে না। মঈনুল হোসেনের সঙ্গে যেটা করা হয়েছিল, বহুজন তাতে হাততালি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তখন ভাবি নাই যে, এ সব খারাপ উদাহরণ তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য। বলতে গেলে উদাহরণ তো অার একটা দুটা নয়, বহু বহু উদাহরণ দেয়া যাবে। রাজনীতির জগত, সংস্কৃতির জগত, শিক্ষাঙ্গন কিছুই বাদ পড়বে না। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর করোনা ধরা পড়লো। কিছু মানুষ খুব নোংরাভাবে বললেন, তিনি ভান করছেন। খুব অশ্লীল মন্তব্য করলেন কেউ কেউ। বহুজন খুশি হয়েছিলেন তাতে। প্রতিবাদ করতে দেখিনি যাঁদের কাছ থেকে প্রতিবাদ আশা করেছিলাম। কারণ আমার শত্রু পক্ষকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করলে আমার কী? বরং আরো করুক। কিন্তু আমার নিজের লোক হলেই প্রতিবাদ করার ইচ্ছা জাগে। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নিন্দা যতোজন করেছেন, হাজার গুণ মানুষ তার চেয়ে তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করেছেন। বন্যার ক্ষেত্রেও সংখ্যাটা তত বেশি না হলেও বহু মানুষ তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করেছেন।
কথাটা হলো ফেসবুকের যেমন অনেক ভালো দিক রয়েছে, কুপ্রভাব রয়েছে অনেক। যখন যা খুশি বলা যায় যেকোনো ভাষায়। কিছু সমালোচনা করার জন্য নিজের যোগ্যতা পরিমাপ করতে হয় না। যা বলছি তা সঠিক বলছি কিনা ভাবতে হয় না। যখন ফেসবুক ছিল না কী ঘটতো? বইপত্র বা যা কিছুই লেখা হোক সকলের সমালোচনা করার সুযোগ ছিল না। নিশ্চয় সেটা ছিল একটা সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সকলে তখন সমালোচনা করার বা যা খুশি মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখাতো না। কারণ কিছু একটা পাঠ করে দু লাইনে ফেসবুকে যা খুশি মন্তব্য করা, আর পত্রিকায় সমালোচনা লিখে পাঠানো এক কথা নয়। ভাষা ব্যবহারে তখন খুব সচেতন হতে হতো, কারণ সকলেই জানতো কুরুচিপূর্ণ কিছু লিখলে পত্রিকায় তা ছাপা হবে না। ভুল বানানে যা কিছু আবোল তাবোল লিখে ফেসবুকে তারকা হওয়া যায়, কিন্তু পত্রপত্রিকায় কিছু লেখা বা সমালোচনা করা বা নিজের দর্শন প্রকাশ করাটা তত সহজ নয়। ভাষাটা অন্তত পরিশীলিত হতে হয়। কারণ পত্রিকার কিছুটা হলেও জবাবদিহিতা থাকে। পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতে হলে সম্পাদকের দৃষ্টিসীমা পার হতে হয়, ফেসবুকের মতো নিজের মন চাইলো আর যা খুশি লিখে ছাপিয়ে দিলাম সেটা হবার উপায় নেই। প্রায় সময় ফেসবুকে দেখা যায়, মতটা কারো সঙ্গে মিলল না বলে গালাগাল আরম্ভ হয়ে যায়। সবার সঙ্গে সবার মত মিলতে হবে কেন। মানুষ কি ছাঁচে গড়া? সব পুরুষ কি একই নারীর প্রেমে পড়ে? নাকি সব নারী একই পুরুষের প্রেমে পড়ে? সকলের দৃষ্টি আলাদা, সুন্দরকে দেখার চোখ আলাদা। সকলের খাবার খাওয়ার, পোশাক পরিধানের রুচি আলাদা। বাঙালীর মেয়ের বেনারসী শাড়ি ছাড়া বিয়ে হয় না, কিন্তু বিশ্বের সকলের কি তাই? বহু বাঙালী মেয়ে রয়েছে বিয়ের দিন বেনারসী না পরিধান না করেই বিয়ে করেছে। ভারতীয়রা টিপ দিচ্ছে কপালে, ভিন্ন দেশের মানুষরা দিচ্ছে না। সবাই এক রকম হতে হবে কেন, কেবল আমার মতোই হবে কেন? নিজে আমি পাঙ্গাশ মাছ, বোয়াল মাছ ইত্যাদি মাছ খাই না, সেজন্য কি বলে দেবো বাকিরা কেউ তা খেতে পারবে না। কপালে টিপ দিলে করোনা হবে, পর্দানশিন থাকলেই করোনা হবে না ব্যাপারটা কি এমন কিছু? সব মানুষ যে একজন আর একজনের মতো নয়, বিশ্বটা সেজন্য অনেক বেশি সুন্দর। না হলে মানুষের বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হতো না। মতাদর্শগত প্রশ্নে সকল মানুষ এক হবে না। মানুষে মানুষে মতবিনিময় হবে। কিন্তু মতের সঙ্গে না মিললে, আমার রুচির সঙ্গে না মিললে, তাকে আক্রমণ করতে হবে কেন? সেটা কি খুব উন্নত মানসিকতা লক্ষণ বলে স্বীকৃতি পাবে?
রেজওয়ানা বন্যা আর জাফরুল্লাহ ভাইর করোনা আক্রমণের বিষয়টা নিয়ে আলাদা করে বলতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের হাতে একজন কালোমানুষের মৃত্যুতে এতবড় আন্দোলনটা কেন হয়েছিল? কারণ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে। করোনা ভাইরাসের প্রভাব না থাকলে কিছুতেই আন্দোলনটা এত প্রভাব ফেলতো না। করোনা ভাইরাসে মানুষ মারা যাচ্ছিলো তখন শ্বাসকষ্টে। সকলে তখন আতঙ্কিত, যদি করোনার সংক্রমণ ঘটে শ্বাসকষ্টে মারা যেতে হবে। শ্বাসকষ্ট বিষয়টাই তখন একটা প্রতীক, একটা মৃত্যুভীতি সারা জগৎ জুড়ে। চিকিৎসকরা তখন চাইছে শ্বাসকষ্টে যেন করোনা রোগীরা মারা না যায়। চিকিৎসকদের সেটাই বড় যুদ্ধ, যেন শ্বাসকষ্টে কাউকে মরতে না হয়। ঠিক তখনি একজন পুলিশ শ্বাসরোধ করে মেরে ফেললো একজন মানুষকে। মৃত্যুর আগে সে বলেছিল ‘আমি শ্বাস নিতে পারছি না’। প্রায় প্রতিটা করোনা রোগী মৃত্যুর আগে ঠিক এমন কিছুই বলতে চাইতো, ‘শ্বাস নিতে পারছি না’। ফলে সেখানে শ্বাসরোধ করে কাউকে মারাটা সেই করোনার আক্রমণ কালে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সহজে মেনে নিতে পারেনি। করোনার শ্বাস রোধ হয়ে মারা যাবার বিরুদ্ধে সেটা একটা প্রতীক ছিল। বিশ্ব যখন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে, যখন মানুষ চাইছে না কেউ শ্বাসকষ্টে মারা যাক; তখন আমার সবচেয়ে বড় শত্রুর করোনা হোক আর শ্বাসকষ্ট পেয়ে সে মারা যাক, এমনটা কি ভাবা যায়! রেজওয়ানা বা জাফরুল্লাহ তো কারো তেমন ব্যক্তিগত বড় শত্রু ছিলেন না। যারাই রেজওয়ানার বা জাফরুল্লাহর বা অন্য কারো করোনা হওয়াতে খুশি হয়েছেন, সকলে তারা ঠিক কি ভুল করেছেন সে বিচার করার ক্ষমতা বা দায় আমার নয়। নিজে আমি নির্ভুল বিচার করার মতো মহান কোন মানুষ নই। কিন্তু যাঁরা আক্রমণ করেছেন, তাঁদের কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন, এটা কি ঠিক একজন মানুষের রোগে খুশি হওয়া? যদি আমার রেজওয়ানা বা জাফরুল্লাহর বিরুদ্ধে নালিশ থাকে, ভিন্ন কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে সমালোচনা করতে পারি। সেটা নিয়ে যুাক্তসঙ্গতভাবে কথা বলতে পারি। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বলে খুশি হওয়া কেন? কালকে কি আমার নিকটতম মানুষটি করোনায় আক্রান্ত হতে পারে না? যুদ্ধের মাঠে কি হয়? শত্রু পক্ষের সৈন্যরা আহত হলে বিপরীত পক্ষের চিকিৎসক কিন্তু শত্রুকে চিকিৎসা দিতে বাধ্য বা সেটাই নিয়ম। খুব রক্তারক্তি কাণ্ডের ভিতরে এটা একটা বিরাট উদারতার জায়গা। চিকিৎসকরা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা কিন্তু তখন ঘৃণা নিয়ে নয়, সকল আন্তরিকতা নিয়েই শত্রুপক্ষের আহত সৈনিকটিকে সেবাটা দিয়ে থাকেন। নিজেদেরকে কি আমরা সেইরকম মানসিকতায় গড়ে তুলতে পারি না? দুজন মানুষের মধ্যে কে সুন্দর? যে চিকিৎসক আহত শত্রুকে চিকিৎসা না দিয়ে মেরে ফেলতে চায়, না যে মানুষটি চিকিৎসা দিয়ে বাঁচাতে চায়? মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার আনন্দটা কতো বড় সেটা বাস্তবে দাঁড়িয়ে টের পাওয়া যায়। শত্রুতা করার, ঘৃণা করার ও একটা নিয়ম থাকে একটা ব্যকরণ থাকে। যদি সেটা খুব উগ্র পথ ধরে, দৃষ্টি কটু লাগে। কথাটা সকলের জন্যই প্রযোজ্য।
পুরো বিষয়টা নিয়ে আরো নানা বক্তব্য ছিল, লেখাটা দীর্ঘ হয়ে যাবার কারণে তা বাতিল করলাম। মূল কথাটা হলো, শেষ বিচারে মানুষ অাশা করে শিল্প সাহিত্য সুস্থ্যরুচির পথ দেখাবে। শিক্ষক অার রাজনীতিকরা সঙ্গী হবেন তাদের।

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান
ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com
মোবাইল +8801716599589
৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
© RP News 24.com 2013-2020
Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি
