সিলেট ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ | ২রা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
প্রকাশিত: ৪:০৫ অপরাহ্ণ, জুন ২৯, ২০২৪
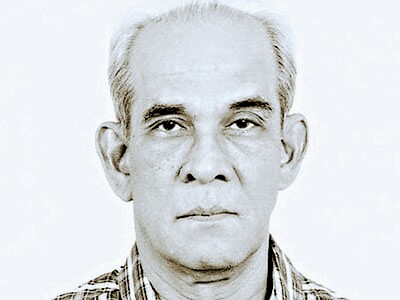
এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের জীবনটা এতই ‘জীবন্ত’ যে, তাঁদের মৃত্যু-সংবাদ মেনে নেয়াটা অন্য দশজনের ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক দুঃসাধ্য। এ ধরনের মানুষের জীবন ও তাঁদের মৃত্যুর মাঝে বৈপীরত্য বা কনট্রাস্টের ছাপটি হয় অন্যদের থেকে অনেক তীক্ষু ও তীব্র। প্রয়াত বন্ধুবর ও কমরেড, অনুজপ্রতিম খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক সম্পর্কে দু কথা লিখতে বসে আমার মাঝে এই অনুভবটিই সর্বাগ্রে জেগে উঠছে। চিন্তা-ভাবনায়, চলন-বলনে, কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে যে মানুষটির মাঝে ‘জীবনের’ দীপ্ত উচ্ছ্বাস সদা-সর্বদা বিশেষরূপ উজ্জ্বলতায় প্রতিবিস্বিত থেকেছে, মৃত্যুর হিম-শীতল নিস্তব্ধতা তাঁর ক্ষেত্রে যেন অনেক বেশি বেমানান বলে অনুভূত হয়। সম্ভবত সে কারণেই, আমি এবং আমার মতো আরো যারা খন্দকার ফারুককে কিছুটা হলেও কাছে থেকে চেনা-জানার সুযোগ পেয়েছে, তাদের পক্ষে তাঁর প্রয়াণের দু দুটি বছর পার হওয়ার পরেও তাঁর সেই অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়া বা ‘রিকনসাইল’ করা এখনও পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠছে না।
খন্দকার ফারুক যে আর জীবিত নেই, মনকে সে বিষয়ে মানিয়ে নেয়া কষ্টকার হচ্ছে আরো এ কারণে যে, তাঁর মৃত্যুর খবরটি সকলের কাছেই উপস্থিত হয়েছিল পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত ও চরম আকস্মিক ভাবে। এটি ছিল অনেকটাই যেন মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের বুক চিড়ে আচমকা দেখা দেয়া বজ্রপাতের মতো। মৃত্যুর সংবাদটি জানতে পারার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত খন্দকার ফারুক সকলের কাছে ছিল প্রচণ্ডভাবে জীবন্ত একজন মানুষের প্রতিচ্ছবি। তাঁর সজীব অস্তিত্ব যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাচ্ছিল, শরীরে রোমাঞ্চ অনুভব করা সম্ভব হচ্ছিল। হঠাৎ করে মাথায় বাজ পড়ার মতো করে দুঃসংবাদটি এলো- খন্দকার ফারুক আর জীবিত নেই।
মৃত্যুর একদিন আগে অনেকটা হঠাৎ করেই খন্দকার ফারুক সস্ত্রীক ব্যাংকক চলে যান। পরে জানা গেছে যে, এর আগে কয়েকদিন তাঁর মুখ দিয়ে অল্প অল্প রক্ত পড়েছিল। এসব কথা তিনি কাউকেই জানাননি। নিজের সমস্যাকে তিনি নিজের মধ্যেই সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। শুধু অসুস্থতার বিষয়ই নয়, নিজের যাবতীয় দুর্ভাবনা-দুঃশ্চিন্তাকে সব ক্ষেত্রেই নিজের মাঝে গুটিয়ে রাখাই ছিল তাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট। ইংরেজিতে একটি কথা আছে “When you laugh, laugh aloud-when you cry, cry alone.”। স্কুল জীবনে স্কাউটিং করার সময় আমরা একটি ইংরেজি গান গাইতাম, যার প্রথম লাইনটি ছিল “Pack up your troubles in your our kit-bag- Smile! Smile!! Smile!!!” অর্থাৎ “আনন্দকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও, দুঃখকে নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখ”। খন্দকার ফারুক আজীবন ছিলেন এই দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা চালিত। গুরুতর অসুস্থতা ও মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও খন্দকার ফারুক সেই পথ ধরেই চলেছিলেন।
খন্দকার ফারুককে আগে বহুবার তার স্ত্রী সাকী খন্দকার ও তাঁর বড় ভাই খন্দকার আব্দুর রহমান সূর্য্যরে চিকিৎসার জন্য ব্যাংককে যেতে হয়েছিল। সেখানকার পথ-ঘাট, হোটেল-হাসপাতাল ইত্যাদি সবই তাঁর পরিচিত ছিল। ব্যাংকক পৌঁছে হোটেলে ওঠার পর পরই তিনি এবার নিজের চিকিৎসার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। সেখানে তিনি তাঁর সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। হাসপাতাল তাঁকে সাথে সাথে ভর্তি করার বদলে, হোটেলে ফেরত পাঠিয়ে রবিবারের ছুটির পরদিন সোমবার চেক-আপের জন্য আসতে বলেছিল। হোটেলে ফিরে লিফ্ট দিয়ে উপরে ওঠার সময় তিনি সেখানেই রক্তবমি করতে করতে এলিয়ে পড়েন। লিফ্ট থেকে তাঁকে কোনো রকমে রুমে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে রক্তবমি করতে করতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টার সুযোগটিও পাওয়া যায়নি। দ্রুতগামী গাড়ির রাজপথ কাঁপানো গতি যেমন ‘হাওয়া ব্রেকার’ দ্বারা আটকে দেয়া হয়, অনেকটা সেভাবেই ফারুকের অফুরন্ত জীবন-শক্তির গতিময়তাও মুহূর্তের মধ্যে অন্তহীন নিশ্চলতায় রূপান্তরিত হয়েছিল।
খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ছিলেন একজন বিপ্লবী। বিপ্লবকে তিনি কেবল কিছু শাস্ত্র-আচার বা দলীয় কর্মকাণ্ডের গণ্ডিতে সীমিত বলে বিবেচনা করতেন না। চলমান বাস্তবতার কাছে, তা সে নিত্যদিনের কোনো তৃণমূলের ছোট্ট ঘটনাই হোক, অথবা হোক তা জাতীয় কিংবা বিশ্বপরিমণ্ডলের কোনো বিষয়, মাথা নত করে তাতে গা ভাসিয়ে দেয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। চোখের সামনের ঘটনা হোক কিংবা হোক তা বৃহত্তর ও বিস্তৃত অঙ্গনের অথবা সুদূরপ্রসারী প্রেক্ষাপটের কোনো ঘটনা- যা অসুন্দর, অন্যায়, যুক্তি-বহির্ভূত, প্রগতি-পরিপন্থী, সব ক্ষেত্রেই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। যে কোনো প্রকৃত বিপ্লবীর ক্ষেত্রে এটি যেমন কি না একটি প্রাথমিক ও আবশ্যিক উপাদান, খন্দকার ফারুকের ক্ষেত্রেও তা ছিল স্বভাবগতভাবে উপস্থিত।
প্রথাবদ্ধ অচলায়তনে তাঁর চিন্তা আবদ্ধ থাকত না। বিপ্লবী প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সেই সহজাত প্রবৃত্তি কেবল তাঁর চিন্তাজগতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত না, তা প্রকাশ পেত তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। বাস্তবতাকে শুধু পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করাই একমাত্র কাজ নয়, একজন বিপ্লবীর আসল কাজ হলো তাকে পরিবর্তন করা- খন্দকার ফারুক এই মার্কসবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তা নিষ্ঠার সাথে প্রয়োগ করতেন। তিনি মার্কসবাদের অনন্ত সৃজনশীলতায় আস্থাশীল ছিলেন। কোনো ‘নেতার’ প্রতি ভক্তির নিদর্শন হিসেবে অথবা অন্ধ আনুগত্য থেকে নয়- বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের যুক্তিগ্রাহ্যতা, ইতিহাসের ধারার পর্যালোচনা ও বাস্তবতা সম্পর্কে নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টির বিচার থেকেই ফারুক মাকর্সবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। স্বভাবগতভাবে খন্দকার ফারুকের ছিল একটি ‘ক্রিটিকাল’ তথা সমালোচনামূলক বৈশিষ্ট। সবকিছুকে তিনি যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করে তার পরে গ্রহণ করতেন। সংশয়গুলো মনের মাঝে রেখে দিতেন। সবসময় সেসবের যৌক্তিকতা যাচাই করে দেখতেন। কিন্তু পার্টির সিদ্ধান্ত আন্তরিকভাবে বাস্তবায়নে বিন্দুমাত্র দ্বিধা কখনও করতেন না। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ শৃংখলা মানা কমরেড।
সত্তরের দশকের শেষ দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পৃক্ত হন এবং এক দশক পরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হন। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ‘পেরেস্ত্রোইকা’, গ্লাসনস্ত’ প্রভৃতি নিয়ে যখন তোলপাড়, তখন তিনি মস্কোতে পার্টি স্কুলে যান। অনেক ভাবনা তাঁকে আলোড়িত করে। দেশ ফেরার পর সিপিবি’র অভ্যন্তরে বিলোপবাদীদের নোংরামি ও আদর্শহীনতা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আহত করে। এ রকম অবস্থায় তিনি পার্টির দায়িত্ব থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেন। আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টিতে সংগঠিত না থাকা সত্ত্বেও তিনি আমৃত্যু মার্কসবাদী আদর্শ ধারণ করেছেন। তিনি শক্তভাবে পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তিমূল ও রাজনৈতিক লাইনের পক্ষে থেকেছেন। তিনি নানাভাবে পার্টিকে সহায়তা দিয়ে গেছেন। বিলোপবাদীদের হামলায় পার্টি যখন আক্রান্ত, তখন তিনি পার্টির পাশে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।
খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক প্রকৃতিগতভাবেই ছিলেন একজন ‘সাধারণের’ মানুষ। ছাত্র, মুটে-মজুর, চাষী, কামার-কুমার-জেলে-মাঝি যাই হোক না কেন, সবাইকে সহজে অন্তরঙ্গ বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং নিজে তাঁদের একজন আপনজন হয়ে ওঠার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। চুম্বকের মতো শক্তি ও গুণাবলী দিয়ে তিনি যে কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে পারতেন। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নেতৃত্ব-ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। তিনি উপর থেকে কারো মদদ পেয়ে নেতা হয়ে ওঠেননি। তাঁর হাতে নেতৃত্ব এসেছে তৃণমূল থেকে, স্বাভাবিকতার ধারায়। ‘নেতা’ হওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা অথবা কলা-কৌশলের আশ্রয় তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। যাঁদের মাঝে তাঁর কাজ তাঁদের আপনজন হয়ে উঠে তাঁদের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার দিকেই ছিল তাঁর মূল দৃষ্টি ও আন্তরিক সাধনা। সে কারণে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন একজন স্বাভাবিক নেতা হিসেবে।
মাত্র ১৫ বছর বয়সে খন্দকার ফারুক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন। পারিবারিক সূত্রেই বামপন্থী রাজনীতির সাথে তার প্রথম সম্পৃক্ততা। সেই চেতনাকে ধারণ করেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। অস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সাথে যোগসূত্র স্থাপনের আগেই তাঁর সামনে অন্য সূত্রে যুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগ এসে পড়েছিল। সে সুযোগ তিনি লুফে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম ও বামপন্থী চেতনা আরো শাণিত হয়।
আমার সঙ্গে খন্দকার ফারুকের পরিচয় আরো পরে। তাঁর দুই বড় ভাই খন্দকার আব্দুর রহমান সূর্য্য ও খন্দকার মোহাম্মদ কামালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা ছিল। আমরা সবাই ছিলাম ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। সেই সূত্রেই তাঁদের সাথে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। পঁচাত্তরের পরে দীর্ঘ কারাজীবন শেষে জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ছাত্র ইউনিয়নের যেসব নেতার নামের সাথে নতুন পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিল খন্দকার ফারুকের নাম। তাঁর নামের সঙ্গে আমাকে যিনি পরিচিত করেছিলেন, তিনি তা করেছিল তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক কথাবার্তা যুক্ত করেই। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, এসব প্রশংসাসূচক কথাগুলো হয়ত বা আমার মনোতুষ্টির জন্য মামুলি কথা। তবে, বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলাম একথা জেনে যে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে খন্দকার ফারুকের কথা বলা হচ্ছে সে আমার শ্রদ্ধেয় সূর্য্য ভাই ও খন্দকার কামাল ভাইয়ের ছোট ভাই। পরে খন্দকার ফারুক নামের সেই তরুণের সাথে দেখা হলো এবং তাঁকে ও তাঁর কাজকর্ম সম্পর্কে আরো ঘনিষ্টভাবে দেখা ও জানার সুযোগ আমার হলো। আমি তাঁর বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলাম। তাঁর অনেক গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হলাম। বুকটা তখন ভরে উঠেছিল এ কথা ভেবে যে, একজন এমন তরুণ বিপ্লবীর দেখা পেলাম যে সাম্যবাদের লাল ঝাণ্ডাকে হাতে তুলে নিয়ে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আপামর ছাত্র-ছাত্রীর আপনজন হয়ে উঠে, তা সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করে চলেছেন। একজন একনিষ্ঠ ও আদর্শ কমরেডকে যে খন্দকার ফারুকের মাঝে খুঁজে পেয়েছি, আনন্দের সাথে সেই উপলব্ধি আমার ভেতর জেগে উঠতে বেশি সময়ের আর প্রয়োজন হয়নি।
খন্দকার ফারুকের ছিল ‘স্বাভাবিক নেতা’ হওয়ার দুর্লভ গুণাবলী। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাঁকে পরপর ৩ বার সরাসরি ভোটে সেখানকার কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত করেছিল। ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক শক্তি-সামর্থ্যের অনুপাতে এটি ছিল আরো অনেক বিস্তৃত সমর্থনের প্রকাশ। তা সম্ভব হয়েছিল খন্দকার ফারুকের প্রর্বতপ্রমাণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে। শিক্ষার্থীরা এভাবে যে তাঁকে তাঁদের নিজেদের একান্ত আপনজন হিসেবে অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল তা ছিল বহুলাংশে খন্দকার ফারুকের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও সর্বোপরি তাঁর অকৃত্রিম ছাত্র-অনুগামীতার কারণে। সেই সাথে একথাও বলা প্রয়োজন যে, নেতা হিসেবে শুধু ছাত্রসমাজের অনুগামী হয়েই তিনি থাকতেন না। তিনি সাধারণ ছাত্রসমাজের পথপ্রদর্শকের কাজটিও দক্ষতার সাথে পালন করতেন। তাঁর এই ‘অগ্রসেনানী হতে পারার’ সক্ষমতাকে ভিত্তি করে তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন করেছেন। “জনগণের সঙ্গে থাকো এবং জনগণের সামনে থাকো”- নেতৃত্বের কর্তব্য সম্পর্কে মহামতি লেনিনের এই শিক্ষা তাঁর মধ্যে লক্ষ্যণীয়ভাবে বিদ্যমান ছিল।
খন্দকার ফারুকের প্রবল জনমুখীনতা এবং তাঁর সমাজতন্ত্রী-সাম্যবাদী বিপ্লবী প্রত্যয় তাঁর শিক্ষাজীবন-উত্তর কর্মকাণ্ডকে এ দেশের ক্ষেতমজুরদের মাঝে কাজ করার পথে এনে সামিল করেছিল। তাঁর জন্য এটিই যেন ছিল অতি স্বাভাবিক। ১৯৮৫ সালে ছাত্র আন্দোলন-সংগঠনের কাজ শেষ হওয়ার আগেই তিনি মনে মনে সার্বক্ষণিক বিপ্লবীর জীবন গ্রহণ এবং ক্ষেতমজুর সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। এর কয়েক বছর আগে, প্রাক্তন ছাত্রনেতা কাজী আকরাম হোসেনসহ আরো কয়েকজন কমরেডকে সাথে নিয়ে আমি ‘ক্ষেতমজুর সমিতি’ নামে সংগঠন গড়ে তুলে দেশব্যাপী ক্ষেতমজুর আন্দোলনের এক বিশাল জাগরণের সূচনা করেছিলাম। খন্দকার ফারুক সেই উত্তাল জাগরণে এসে যোগ দিয়েছিলেন। তৃণমূলের সেই ক্ষেতমজুর জাগরণ পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট সংগঠক কেন্দ্রে না থাকার যে পরিস্থিতি সেসময় বিরাজ করছিল, খন্দকার ফারুকের সেখানে এসে যুক্ত হওয়ায় সেই ঘাটতি বহুলাংশে পূরণ হয়েছিল। তাঁর সম্পৃক্ততার ফলে ক্ষেতমজুরদের খাস জমির আন্দোলন নতুন গতিবেগ পেয়েছিল। ক্ষেতমজুর আন্দোলনকে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার বাইরেও স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামসহ জাতীয় বিভিন্ন ইস্যু, নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্ম, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সাথে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। সংগঠনিক কাজকেও সুশৃঙ্খল ও দক্ষ করে একটি উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। খন্দকার ফারুক হয়ে উঠেছিলেন ক্ষেতমজুর সমিতির সে সময়কার মূল কেন্দ্রীয় টিমের একটি প্রধান স্তম্ভ।
ঢাকায় বসে টেকনিক্যাল কাজে যতটা না খন্দকার ফারুক ব্যস্ত থাকতেন, তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতেন গ্রামে-গঞ্জে ক্ষেতমজুরদের মাঝে পড়ে থাকতে। এ কাজেই তিনি আনন্দ পেতেন বেশি। আমাদের মতোই তিনি মাসে এক-দুবার ১০-১২ দিনের লম্বা টানা সফরে ঢাকা থেকে বেরিয়ে পড়তেন। ছুটে যেতেন তৃণমূলের প্রত্যক্ষ আন্দোলনের এলাকায়। স্থানীয় পর্যায়ের সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। তাছাড়াও ক্ষেতমজুর সমিতির তৃণমূলের গ্রাম কমিটি থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা স্তরে সাংগঠনিক কাজ তাঁকে টেনে নিয়ে যেত দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে। কখনও কখনও রাত কাটাতে হতো ক্ষেতমজুরের জীর্ণ কুটিরে। দিনের পর দিন পার করে দিতে হতো এক কাপড়ে।
নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে ক্ষেতমজুর সমিতিকে তার বিপ্লবী চরিত্র থেকে একটি সংস্কারবাদী ধারায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়। কায়দা করে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয় সংস্কারবাদীরা। এনজিও ব্যুরোতে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সংগঠনটিকে একটি এনজিওতে পরিণত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির বিলোপবাদী নেতৃত্ব এই প্রচেষ্টায় মদদ দেয়। তারা শুরু করে নোংরা ষড়যন্ত্র। এসব নোংরামি খন্দকার ফারুককে প্রবলভাবে আহত, হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এসব নোংরামির মাঝে থেকে তা মোকাবেলা করার মতো প্রবৃত্তি খন্দকার ফারুকের মাঝে ছিল না। সে সময়টিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ঘটনাও বিরাট ধাক্কা হিসেবে তাঁকে আঘাত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করে একটি ‘রূপান্তরিত’ দল হিসেবে তাকে পরিচালনার জন্য পার্টির বিলোপবাদী নেতৃত্ব ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা শুরু করেছিল। খন্দকার ফারুকের কাছে এসব কর্মকাণ্ড ছিল অসহ্য। সার্বিক অবস্থায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রচণ্ডভাবে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দ্রুতই নিজেকে এসব থেকে সরিয়ে নিতে থাকেন। সার্বক্ষণিক বিপ্লবীর জীবন ছেড়ে তিনি পেশায় জড়িত হয়ে পড়েন।
এভাবে শুরু হয়ে যায় খন্দকার ফারুকের জীবনের প্রায় দুই দশক ধরে চলা তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়। কিছু সময় এদিকে-ওদিকে চাকরি করে পার করার পর তিনি নিজেই তাঁর নিজস্ব রেডিমেড টেক্সটাইলের ‘বাইং হাইজ’ স্থাপন করেন। সে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়। খন্দকার ফারুকের হাতে টাকা আসতে থাকে। কিন্তু তার ফলে তাঁর অন্তরের গভীরে লালিত বিপ্লবী মন ও মানসিকতাতে মোটেও চিড় ধরেনি। পার্টির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে তিনি নিয়মিত সহযোগিতা করতেন। পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়ের জন্য অথবা কোনো বিষয়ে অভিমত জানানোর জন্য ডাকলেই চলে আসতেন। খন্দকার ফারুকের অন্তহীন মানবিকতা কখনও শুকিয়ে যায়নি। অসংখ্য মানুষকে সে হাত খুলে সাহায্য করেছে। তাঁর এসব সহায়তার কাজ বেশি কাউকে তিনি জানতে দিতেন না। তিনি ছিলেন নিরব দাতা। স্ত্রীর ও বড় ভাইয়ের ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য শুধু উজাড় করে অর্থ ব্যয়ই নয়, নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।
খন্দকার ফারুকের ব্যবহার ছিল অমায়িক। এমনিতে সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন। তিনি খুবই মিশুক ও আলাপী ছিলেন। কিন্তু কারো মাঝের নীচুতা, সংকীর্ণতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কোনো মানুষ সম্পর্কে মনে মনে চরম বিরক্ত হয়ে থাকলেও, সচরাচর তা তিনি প্রকাশ করতেন না। বেশি হলে কথাবার্তা কমিয়ে দিয়ে নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে নিতেন। তাঁর গম্ভীর দরাজ কণ্ঠ তাঁকে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। সেই কণ্ঠস্বর তুলে ধরত তাঁর মনের দৃঢ়তাকে। তাঁর সেই বর্জ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া আহবান অগ্রাহ্য করবে, এমন মানুষ কমই ছিল।
কমরেড খন্দকার মোহাম্মদ ফরুক, লাল সালাম!
#
মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সাবেক সভাপতি
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
(২৯ জুন ২০১৭)

সম্পাদক : সৈয়দ আমিরুজ্জামান
ইমেইল : rpnewsbd@gmail.com
মোবাইল +8801716599589
৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।
© RP News 24.com 2013-2020
Design and developed by ওয়েব নেষ্ট বিডি
